রুশ সংস্কৃতি একটি স্বতন্ত্র সত্তা — পশ্চিমা বিশ্বের থেকে ভিন্ন এক ধারণা — এই ভাবনাটি বর্তমানে বহু স্তরে প্রতিরোধের মুখে পড়েছে: ইতিহাসলেখন, সমাজ-রাজনীতি, এবং ভূ-রাজনৈতিক স্তরে। যদি রাশিয়া সত্যিই একটি অনন্য সাংস্কৃতিক সত্তা হয় — এক সভ্যতা বা সভ্যতাগত ব্লক — এবং আজ তার নিয়তি অস্বীকার করা হচ্ছে, তবে এর গভীর অস্তিত্বগত প্রভাব পড়বে কেবল রাশিয়ার ওপর নয়, বরং রুশ ভূভাগের সীমান্তঘেঁষা অন্যান্য বিশ্বের ওপরও।
যখন ইতিহাসকে এমন এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় যেখানে প্রতিটি সংস্কৃতির নিজের মতো করে অস্তিত্ব বজায় রাখার অধিকারকে স্বীকার করা হয় — যেখানে প্রতিটি সংস্কৃতি তাদের অবচেতন ভাবনাগুলিকে সচেতন প্রকাশে রূপ দেয়, তাদের নিজস্ব সত্য ও রূপকে বিশ্বের জন্য একপ্রকার উপহার হিসেবে ভাগ করে নেয় — তখন এই উপলব্ধি আজকের অস্থির ও উদ্বেল ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা বোঝার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে ওঠে।
এই অস্থিরতা, অন্তত রুশ বিশ্বের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, এক দীর্ঘদিন ধরে অস্বীকৃত সংস্কৃতির প্রতিফলন। সেই অস্বীকৃতি এসেছে কখনও রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহ থেকে — যেমন জার পিটার দ্য গ্রেটের শাসনামলে রাশিয়ার নিয়তি পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া — কিংবা পরপর তাতার আক্রমণগুলোর মাধ্যমে, বা এমনকি বাইজেন্টাইন বুদ্ধিবৃত্তিক-আধ্যাত্মিক প্রভাবের মাধ্যমে।
পরবর্তীকালে বলশেভিক বিপ্লবের পর মার্কসবাদী আদর্শ রুশ আত্মার যে উলটপালট ঘটায়, এবং বর্তমানে ন্যাটোর রুশ সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ — এই দুই ঘটনাই রাশিয়ার সাংস্কৃতিক বিকাশের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত হুমকির উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
আজ রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া — সেটা হোক পশ্চিমা সার্বজনীনতার বিকল্প এক মডেল উপস্থাপন করা, যেমন বৈশ্বিক ব্যবস্থায় BRICS ও বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থার প্রচার, যা প্রত্যেক সাংস্কৃতিক ব্লকের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়, অথবা ন্যাটোর আগ্রাসনের জবাব হিসেবে সামরিক অভিযান — এই সবই এক প্রকার “সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা” বা “cultural immune system”-এর প্রতিফলন।
তবুও, যেমন নিকোলাই বেরদিয়ায়েভ একসময় বলেছিলেন, রুশ ইতিহাসের এক পর্যালোচনা দেখায় যে এটি “সবচেয়ে বেদনাদায়ক ইতিহাসগুলির একটি”। আমি যোগ করব — বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের (শীতল যুদ্ধ ও পরবর্তী সময়) এবং একবিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলিকে বিবেচনা করলে — বেরদিয়ায়েভের এই বক্তব্য রাশিয়ার অতীত, বর্তমান এবং সম্ভবত ভবিষ্যতেরও এক চিরন্তন বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিভাত হয়।
আজ প্রায় সবার কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে বিশ্ব এক নতুন বৈশ্বিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছে — এমন এক পরিবর্তন যা বহু সাংস্কৃতিক ব্লকের বাস্তবতাকে পুনর্গঠন করবে। এই রূপান্তরের অগ্রভাগে রয়েছে রুশ বিশ্ব — এবং রাশিয়া ও পশ্চিমের সংঘর্ষ তাই এক বিশ্ব-ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
পশ্চিমের অনেকেই এখনো এই বাস্তবতা এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যতের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছেন না—যেখানে রাশিয়া, একটি সংস্কৃতি হিসেবে, নিজের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য ও নিয়তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে; যেমন একসময় পশ্চিম নিজস্ব গতিপথে এগিয়ে গিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে নিজের নিয়তিকে পূর্ণতা দিয়েছিল। রাশিয়ার এই স্বতন্ত্রতাকে অস্বীকার করার প্রবণতাটি সরাসরি যুক্ত পশ্চিমা “ইউনিভার্সালিজম” ধারণার সঙ্গে—একটি বৈশিষ্ট্য যা পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্তর্গত, এবং আলোকায়ন যুগের পর থেকে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।
এই বৈশিষ্ট্যটি পশ্চিমা সংস্কৃতির ইতিহাসজুড়ে প্রসারিত ও রূপান্তরমূলক প্রকৃতির সঙ্গেও সরাসরি সম্পর্কিত। আলোকায়ন যুগের দর্শনগুলো, যা প্রথমে পশ্চিমা সংস্কৃতির অবচেতনে ছিল, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সেই সংস্কৃতির সচেতন রূপে具 বাস্তবায়িত হয়—এবং তা পশ্চিমা পররাষ্ট্রনীতি ও সমাজ-রাজনৈতিক গতিশীলতার মধ্যে সরাসরি প্রতিফলিত হয়। অন্যভাবে বললে, পশ্চিমা বিশ্ব আলোকায়ন যুগের সূচনা থেকেই এত গভীরভাবে প্রভাবিত যে আজকের যুগে সেটি প্রায় উপেক্ষিত থাকে।
ইমানুয়েল কান্টের “চিরস্থায়ী শান্তি” ধারণাটি, যা তিনি তাঁর ইতিহাস দর্শনে উপস্থাপন করেছিলেন, বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা বৈশ্বিক ব্যবস্থার উত্থানের মাধ্যমে বাস্তব রূপ পায়। যদিও কান্টের এই ইতিহাস দর্শন অনেকের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়, তবু এটি এমন এক দর্শন যা অ-পশ্চিমা সাংস্কৃতিক সত্তাগুলোর অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে।
কান্টের সমস্যাটি ছিল এই যে তিনি ইতিহাস দর্শনের সঙ্গে নৈতিকতাকে যুক্ত করেছিলেন এক সার্বজনীন (universalist) দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে—অর্থাৎ মানবজাতিকে “একক সমষ্টি” হিসেবে দেখা, যা সমাজগতভাবে একত্রিত universorum হিসেবে বিদ্যমান। ফলে, তিনি এমন এক ইতিহাস-দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যা মানবজাতিকে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও জাতির এক বহুত্ববাদী রূপে দেখে—যারা একে অপরের থেকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্নভাবে (singulorum) কার্যকর থাকে।
মানবজাতি ও তার বিভিন্ন সংস্কৃতিকে “একক সমষ্টি” হিসেবে ধরার সমস্যা স্পষ্ট হয় যখন প্রশ্ন তোলা হয়—“মানবজাতি” বলতে আসলে কার দৃষ্টিভঙ্গির মানবজাতিকে বোঝানো হচ্ছে?
কান্টের দ্বিতীয় বড় ভুল, যা তাঁর ইতিহাসে নৈতিকতার সংমিশ্রণের ফল, ছিল ইতিহাসের ওপর এক কঠোর সরলরৈখিক (linear) কাঠামো আরোপ করা। এই কান্টীয় সার্বজনীন সরলরৈখিক ইতিহাস-ধারণা এমন যেকোনো সংস্কৃতি বা জাতিকে বাদ দিয়ে দেয় যারা এই কাঠামোর সঙ্গে খাপ খায় না, অথবা তাদেরকে জোরপূর্বক সেই কাঠামোর ভেতরে টেনে আনে। এই একই সমস্যা পরবর্তীতে গিওর্গ ভিলহেল্ম হেগেলের ইতিহাস দর্শনেও বজায় থাকে, এবং আরও চরমভাবে প্রকাশ পায় তাঁর Lectures on the Philosophy of World History (১৮৩৭) গ্রন্থে।
কান্টীয় ইতিহাস দর্শনের মৌলিক সমস্যা হলো—এর সরলরৈখিক ইতিহাস-ধারণা ও তার সঙ্গে যুক্ত নৈতিক দর্শন উভয়ই সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমা চিন্তাধারার অন্তর্গত এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। তবু, এই ধারণাগুলো আলোকায়ন যুগ থেকে পশ্চিমা সম্মিলিত মানসচেতনতার (collective psyche) অংশ হয়ে গেছে, এবং তা গড়ে তুলেছে তাদের ইতিহাসলেখন, ইতিহাস দর্শন, এবং পরবর্তীতে পররাষ্ট্রনীতির দিকনির্দেশ।
তবে মনে রাখতে হবে, আলোকায়ন যুগের সেই নির্দিষ্ট সময় থেকে এটি একমাত্র উদীয়মান বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা ছিল না; এর বিপরীত ধারাও গড়ে ওঠে রোমান্টিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, যা পরবর্তীতে “কাউন্টার-এনলাইটেনমেন্ট” নামে পরিচিত হয়।
এই ধারাটি ইতিহাস সম্পর্কে এমন এক দর্শন গড়ে তোলে যা প্রায় আলোকায়নের বিপরীত—এটি সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে আপেক্ষিকতার (relativism) ভিত্তিতে দেখে, যেমনটি ইয়োহান গটফ্রিড হার্ডারের রচনাগুলোতে দেখা যায়। যদিও “কাউন্টার-এনলাইটেনমেন্ট” ধারাটি আলোকায়নের প্রভাবের কারণে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে যথাযথ রাজনৈতিক প্রকাশ পায়নি, তবু এটি এমন কিছু দার্শনিক আন্দোলনের পূর্বসূরি হয়ে ওঠে যা পরবর্তীতে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলে।
<img src ='https://cms.thepapyrusbd.com/public/storage/inside-article-image/fbq0moive.jpg'>
হার্ডারের ভাবধারা পরবর্তীতে ওসওয়াল্ড স্পেংলারের রচনায় ধারাবাহিকতা পায়—যিনি একইভাবে এমন এক ইতিহাস দর্শন গ্রহণ করেন যা সংস্কৃতিগুলোকে পৃথক ও আপেক্ষিকভাবে দেখে।
যদিও “কাউন্টার-এনলাইটেনমেন্ট” শেষ পর্যন্ত পশ্চিমা একাডেমিক পরিমণ্ডলে দমন ও বর্জিত হয়েছিল, এটি রুশ সংস্কৃতি সম্পর্কে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছিল।
স্লাভোফাইল চিন্তকদের মতো, হার্ডার ও স্পেংলার উভয়েই রাশিয়াকে একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি হিসেবে দেখেছিলেন—যা পশ্চিম ও পূর্ব উভয়ের থেকেই আলাদা। তাঁদের ইতিহাস-দর্শন ছিল বিনয়পূর্ণ; তারা সময়কে শুধুমাত্র সরলরৈখিক নয়, বরং চক্রাকারে (cyclical) দেখেছিলেন—যা সময়ের দিকনির্দেশের সঙ্গে একত্রে চলে। এর বিপরীতে কান্ট ও আলোকায়ন চিন্তকরা সময়কে কেবল সরলরেখায় দেখেছিলেন, যা স্বাভাবিকভাবেই একপ্রকার সাংস্কৃতিক ঔদ্ধত্যে (cultural hubris) রূপ নেয়।
ভাবা যায়, যদি “কাউন্টার-এনলাইটেনমেন্ট” আন্দোলন আলোকায়নের পরিবর্তে পশ্চিমে মূলধারায় পরিণত হতো, তাহলে আজকের পশ্চিমা বিশ্ব কেমন হতো। একটিই বিষয় নিশ্চিত — তাহলে রুশ সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিমের এমন সরাসরি সংঘাত হয়তো ঘটত না।
পশ্চিমা চিন্তার ইতিহাসে আলোকায়নের ধারণাগুলোর বিকাশ অনুসরণ করলে আমরা এসে পৌঁছাই আইজাইয়া বার্লিনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে—যেখানে তিনি কান্টের কিছু ধারণাকে ব্যবহার (এবং অস্ত্রায়িত) করেন রুশ সংস্কৃতিকে আক্রমণ করার জন্য, “উদারতাবাদ”-এর নামে। রুশ সংস্কৃতির এই তীব্র সমালোচনাটি বার্লিন উপস্থাপন করেছিলেন এক ধারাবাহিক বক্তৃতায়, যার শিরোনাম ছিল “The Russian Obsession with History and Historicism”। আমার বিচার অনুযায়ী, এই বক্তৃতাগুলো কেবল বিংশ শতাব্দীর পশ্চিমা ইতিহাস-দর্শনের অবস্থাই প্রকাশ করে না—যেখানে ইতিহাস ও অতীতকে ধীরে ধীরে অস্তিত্বগতভাবে (ontologically) প্রত্যাখ্যান করা শুরু হয়েছিল—বরং তা প্রতিফলিত করে পশ্চিমা সংস্কৃতির নিজস্ব মানসিক অস্থিরতাকে, যা তারা অন্য সুস্থ সংস্কৃতির ওপর প্রক্ষেপণ করেছিল, যেসব সংস্কৃতি অতীতের প্রতি এমন সমষ্টিগত অসহিষ্ণুতা ভোগ করে না।
বিরূপভাবে, বার্লিন যখন পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে “রুসোফোবিয়া” বপন করছিলেন, তখনই তিনি এই বক্তৃতাগুলোর একটি দেন ১৯৬৭ সালে University of Sussex-এ—যে বিশ্ববিদ্যালয়টি আজ “UK-এর সবচেয়ে woke ক্যাম্পাস” হিসেবে পরিচিত। আমি নিজেই ২০১৯ সালে সেখানে আমার এক স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছি, এবং প্রায় বিদ্রূপাত্মকভাবে বলতে হয়—গত কয়েক বছর আমি আমার লেখালেখির মাধ্যমে বার্লিনের রুশ সংস্কৃতি ও ইতিহাস-দর্শন সম্পর্কিত সমালোচনার বিরুদ্ধে যুক্তি তৈরি করছি, অথচ আমি তখনই পড়াশোনা করছিলাম সেই গ্রন্থাগারে যেখানে বার্লিনের আসল বক্তৃতার রেকর্ডিং সংরক্ষিত আছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পশ্চিমা সংস্কৃতিতে যে একপ্রকার “বাধ্যতামূলক বিস্মৃতি” (enforced amnesia)তৈরি হয়েছিল, বার্লিন তারই প্রতিফলন ঘটান। তিনি যুক্তি দেন যে ইতিহাস-দর্শন সম্পর্কিত রচনাগুলো—যেমন মার্কস, হেগেল, স্পেংলার, হার্ডার, ভিকো, বাইবেল, বা অন্যান্য অনুমাননির্ভর ঐতিহাসিক তত্ত্ব—এসবকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত নয়; এগুলো কেবল “ছদ্মবিজ্ঞান” (pseudo-discipline)-এর ফলাফল হিসেবে দেখা উচিত।
বার্লিনের কাছে “history” বা “historicism” বলতে বোঝায় এমন এক বিশ্বাস যেখানে ইতিহাসকে অতীত–বর্তমান–ভবিষ্যতের ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখা হয়—অর্থাৎ এই বিশ্বাস যে ইতিহাসের একটি অর্থ আছে, এবং মানবজাতি বা সংস্কৃতিগুলোর ইতিহাসে একটি নিয়তি (destiny) বিদ্যমান। অন্যভাবে বললে, এখানে ইতিহাস বা historicism মানে “speculative philosophy of history”-ই।
বার্লিন এই ধারণাটিকে ভ্রান্ত বলে মনে করেন। তাঁর কাছে ইতিহাসের কোনো নিজস্ব দর্শন নেই, কোনো অর্থও নেই—অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যৎ পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। ইতিহাসের ভেতরে ক্রিয়াশীল সত্তাগুলো—সংস্কৃতি, সভ্যতা, বা মানুষ—তাদেরও কোনো অস্তিত্বগত নিয়তি নেই, কারণ না তাদের অস্তিত্বকে প্রমাণ করা যায় বাস্তবভাবে (empirically), না সেই মেটাফিজিক্যাল জগৎকে যা Volkgeister (জাতিগত আত্মা), সাংস্কৃতিক জীব, বা সভ্যতার জন্ম দেয়।
এটি নিঃসন্দেহে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, এবং বার্লিন সেটিকে পশ্চিমা সংস্কৃতির ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—এবং আমার মতে, তিনি তা অনেকাংশেই সফলভাবে করেছিলেন। পশ্চিমা সংস্কৃতি তখনই অতীত ও ইতিহাসের অস্বীকারের পথে চলছিল, যা পরবর্তীতে পোস্টমডার্ন ইতিহাস-দর্শন ও ইতিহাসলেখনের উত্থানে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়।
বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। কিন্তু বার্লিনের মূল সমস্যা ছিল তাঁর পদ্ধতি এবং এসব সংবেদনশীল বিষয়ের ওপর তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।
বার্লিনের মতে, রুশরা ইতিহাসে তাদের নিজস্ব ভূমিকা ও নিয়তি নিয়ে একধরনের জন্মগত আসক্তিতে (obsession) ভুগে থাকে—যদিও সেটা সরাসরি প্রকাশ না-ও পেতে পারে, কিন্তু তা তাদের চিন্তায় এবং সমাজে পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়।
বার্লিন মনে করতেন, এই আসক্তি বিপজ্জনক, কারণ নির্দিষ্ট ইতিহাস-দর্শনের প্রতি বিশ্বাস এবং সেই দর্শন থেকে উদ্ভূত ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। তাঁর কাছে এই পরিণতি ইতিহাস-দর্শনের শক্তির প্রতিফলন নয়; বরং তিনি এগুলোকে self-fulfilling prophecies হিসেবে দেখতেন—অর্থাৎ যে ভবিষ্যদ্বাণী নিজেই নিজের বাস্তবায়ন ঘটায়।
বার্লিনকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছিল এই যে, রাশিয়ায় বিভিন্ন ইতিহাস-দর্শন সত্যিই রাজনৈতিক বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে—কারণ রুশ জনগণ ও চিন্তকরা এসব ধারণাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু এখানেই বার্লিনের যুক্তিতে এক ধরনের জ্ঞানগত পক্ষপাত (cognitive bias) স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
কারণ, বার্লিনের নিজস্ব মেটাফিজিক্স-বর্জনই আসলে একটি মেটাফিজিক্যাল অনুমান। ফলে, এক বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি—যা মেটাফিজিক্সকে স্বীকার করে—এই দর্শনগুলোর বাস্তবায়নকে কেবল ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা বা দার্শনিক সত্য হিসেবে দেখতে পারে। তাই যেখানে বার্লিন এগুলোকে “self-fulfilling prophecy” বলেছিলেন, আমি বলব—এগুলো সত্য হয়েছে, কারণ এগুলো সত্যই ছিল।
এই ভ্রান্ত দ্বৈততা আরও স্পষ্ট হয় যখন বার্লিন পশ্চিমকেন্দ্রিক ভঙ্গিতে যুক্তি দেন যে, পশ্চিম এখন ইতিহাস ও historicism-এর বিশ্বাস থেকে “উত্তীর্ণ” হয়েছে। তাঁদের কাছে এসব দর্শন কেবল “বুদ্ধিজীবীদের আলাপচারিতা”, যার কোনো বাস্তব সামাজিক প্রভাব নেই।
বার্লিনের মতে, পশ্চিম এসব ধারণার ওপরে উঠে গেছে—তারা “ইতিহাসে বেশি পরিপক্ব”—এবং তাই তারা এসব ধারণা থেকে “রক্ষিত”। এই যুক্তি আসলে আগেই আলোচিত কান্টীয় ইউনিভার্সালিজম-এরই আরেক প্রকাশ, যা শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতিগুলোর মধ্যে এক ধরনের শ্রেণিবিন্যাস (hierarchy) সৃষ্টি করে।
বার্লিন প্রকাশ্যেই বলেন, “রাশিয়া পশ্চিমের মহোৎসবে এক দেরিতে আগত অতিথি (latecomer)। তারা বিশ্বশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় অনেক পরে, উনিশ শতকের শুরুতে।”
<img src ='https://cms.thepapyrusbd.com/public/storage/inside-article-image/6rsi8hnrv.JPG'>
রাশিয়া ইতিহাসে তুলনামূলকভাবে “যুবা” জাতি বা সংস্কৃতি—এ কথা সত্য, কিন্তু বার্লিন যেভাবে বলেছিলেন, “পশ্চিমের ভোজে দেরিতে এসেছে”—এটি ভ্রান্ত। কারণ ইতিহাস কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা সংস্কৃতির সম্পত্তি নয়; বরং ইতিহাসই জাতি ও সংস্কৃতিগুলোর বিকাশের চালিকাশক্তি।
এটাই সেই পশ্চিমা প্রবণতা, যা বিমূর্ত বা বাস্তব—সবকিছুকে নিজের বলে দাবি করে, এমনকি ইতিহাসকেও, যেন ইতিহাস নিজেই পশ্চিমের অস্তিত্বগত সত্তা।
বার্লিনের বক্তৃতাগুলো রুশ ইতিহাসে পরস্পরবিরোধী ইতিহাস-দর্শনগুলোর সংঘাতও তুলে ধরে—যেখানে ইতিহাসের ধারা, দিকনির্দেশ, এবং তার অর্থ নিয়ে এক তীব্র বিতর্ক চলে আসছে রাজতন্ত্রী, মার্কসবাদী, স্লাভোফাইল এবং পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যে। এই সব ধারাই আসলে ইতিহাস-আসক্ত এক সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ।
রুশ সংস্কৃতির প্রতিটি এই ধারাই নিজস্ব ইতিহাস-দর্শন বহন করেছে, যা কোনো এক পর্যায়ে বাস্তবে রূপ নিয়েছে। কিন্তু যদি আমরা ইতিহাস-দর্শনকে একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হিসেবে মেনে নিই, তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেখা যায়।
বার্লিন যেটাকে ভয় পেতেন, সেটিই সত্য ছিল—রুশ জনগণের কাছে ইতিহাস ছিল এক অস্তিত্বগত বাস্তবতা, এবং এটি কোনো “ত্রুটি” নয়, বরং এক সংস্কৃতির জীবন্ত ভবিষ্যতের সূচক।
ইতিহাসে অর্থ, প্যাটার্ন, দিকনির্দেশ, ও নিয়তি সম্পর্কে রুশদের গভীর কৌতূহল প্রকাশ করে এক নবজাগ্রত সংস্কৃতিকে—যা এখনো বিশ্বের ইতিহাসমঞ্চে নিজের আত্ম-অবচেতন থেকে জেগে উঠছে।
বার্লিন যে স্লাভোফাইল ইতিহাস-দর্শনকে ব্যঙ্গ করেছিলেন—যেখানে রাশিয়াকে এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি হিসেবে দেখা হয়—তা আসলে এক “মহাকাব্যিক ঐক্যবদ্ধ ইতিহাসচিত্র”-এর প্রতিফলন, যা প্রত্যেক নবজাত সংস্কৃতির সূচনালগ্নে দেখা যায়; স্পেংলারের ভাষায়, এটি “সুপার-পার্সোনাল ঐক্য ও পরিপূর্ণতা”-র প্রকাশ।
রাশিয়ায় এই “ইতিহাস-আসক্তি”-র দুই রূপ—একদিকে পশ্চিমমুখী রুশ চিন্তক, অন্যদিকে স্লাভোফাইল—এই দ্বৈততাকেই স্পেংলার বলেছেন “two faces of Russia”, এবং বেরদিয়ায়েভ বলেছেন রুশ আত্মার “অন্তর্নিহিত দ্বৈততা” (inner polarity), যা পূর্ব ও পশ্চিমের সংঘর্ষকে সমন্বয় করার চেষ্টার ফল।
এই দ্বৈততা রাশিয়ার “দ্বৈত বিশ্বাস” (double belief)-এ প্রতিফলিত হয়—যেখানে অর্থডক্স খ্রিষ্টান ধর্মের পাশাপাশি এক অবচেতন লোকধর্ম (paganism) সহাবস্থান করে।
যে কোনো পশ্চিমা দর্শন, যা সাংস্কৃতিক সার্বজনীনতাকে (cultural universalism) পূর্বশর্ত হিসেবে ধরে নেয়, রাশিয়ার সত্যকে বুঝতে সক্ষম নয়। ফলে রুশ সংস্কৃতির জটিলতা এবং এর সমাজ-রাজনৈতিক প্রবাহগুলোকে অতিসরলীকরণ করা হয়—যেমনটি বার্লিনের বক্তৃতাগুলো করেছে।
অতএব, যেখানে বার্লিন স্লাভোফাইল ও পশ্চিমমুখী রুশ চিন্তকদের বিভাজনকে তুচ্ছ বলে মনে করেছিলেন, বেরদিয়ায়েভ সেটিকে রুশ আত্মার গভীর দ্বৈততার নিখুঁত প্রতিফলন হিসেবে দেখেছিলেন।
বেরদিয়ায়েভের মতে, এই দ্বৈততা রুশ সংস্কৃতির এক চিরন্তন বৈশিষ্ট্য—যা রুশ আত্মার অবস্থান থেকে জন্ম নিয়েছে বিশ্বের ইতিহাসের “দুই স্রোতের”—পূর্ব ও পশ্চিমের—মাঝখানে।
স্পেংলারের ভাষায়, পশ্চিমকেন্দ্রিক ভূগোলের ভুল ধারণা ইতিহাসকে বিকৃত করে—যখন ইউরোপ বা আফ্রিকার মতো মহাদেশগুলোকে কেবল রাজনৈতিক সীমারেখায় সংজ্ঞায়িত করা হয়, অথচ উপেক্ষা করা হয় তাদের জটিল সাংস্কৃতিক গতিবিধি ও প্রকৃত, জৈবিক সীমা, যা চিরস্থায়ী পরিবেশগত (ecological) বাস্তবতার মাধ্যমে নির্ধারিত।
এই ভ্রান্ত ভূগোলের পরিবর্তে, ভৌগোলিক দিকনির্দেশ (geographic directions)-ই ইতিহাস, জীবন, ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অর্থবহ।
স্পেংলার বলেছিলেন, “পূর্ব–পশ্চিম দ্বৈততা এমন ধারণা, যার ভেতরেই প্রকৃত ইতিহাস নিহিত আছে।”
অতএব, ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রকৃতি নিয়ে আলোচনায় এখানে দুটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি বা “প্যারাডাইম” একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। একদিকে আছে এমন এক প্যারাডাইম, যা ইতিহাস ও অতীতের অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং সংস্কৃতিকে অস্তিত্বগত (ontological) সত্তা হিসেবে স্বীকার করে না। এই ধারা মূলত আলোকায়ন যুগ (Enlightenment) থেকে উৎসারিত, যা বিংশ শতাব্দী জুড়ে পাশ্চাত্য চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে, আরেকটি প্যারাডাইম রয়েছে, যা ইতিহাস ও অতীতের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং সংস্কৃতিকে এক বাস্তব, অস্তিত্বশীল সত্তা হিসেবে মেনে নেয়। এই দ্বিতীয় ধারার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় বিরোধী-আলোকায়ন (Counter-Enlightenment) চিন্তায় — বিশেষ করে হার্ডার (Herder)-এর ইতিহাস-দর্শন ও নিউটনীয় বিজ্ঞানের পরিবর্তে গ্যোথীয় (Goethean) বিজ্ঞানে।
রাশিয়ায় এই নির্দিষ্ট আপেক্ষিকতাবাদী প্যারাডাইমটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় স্লাভোফাইল চিন্তাবিদদের কাজে — এখান থেকেই বার্লিনের “রাশিয়ানদের ইতিহাস ও হিস্টোরিসিজম নিয়ে আবেগ” ধারণাটি জন্ম নেয়।
১৯৬২ সালে থমাস কুন তাঁর The Structure of Scientific Revolutionsগ্রন্থে বলেন, কোনো প্যারাডাইম স্থির বা সরলরেখীয় নয়; বরং ইতিহাসের ধারায় এরা ঘূর্ণায়মান ও পরিবর্তনশীল। একটি যুগে যা “স্বাভাবিক বিজ্ঞান” বলে বিবেচিত হয়, ভবিষ্যতের কোনো এক সময়ে সেটিই আবার নতুন প্যারাডাইম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এক প্যারাডাইম থেকে আরেক প্যারাডাইমে রূপান্তরকেই কুন “প্যারাডাইম শিফট” বা “বৈজ্ঞানিক বিপ্লব” বলেছেন।
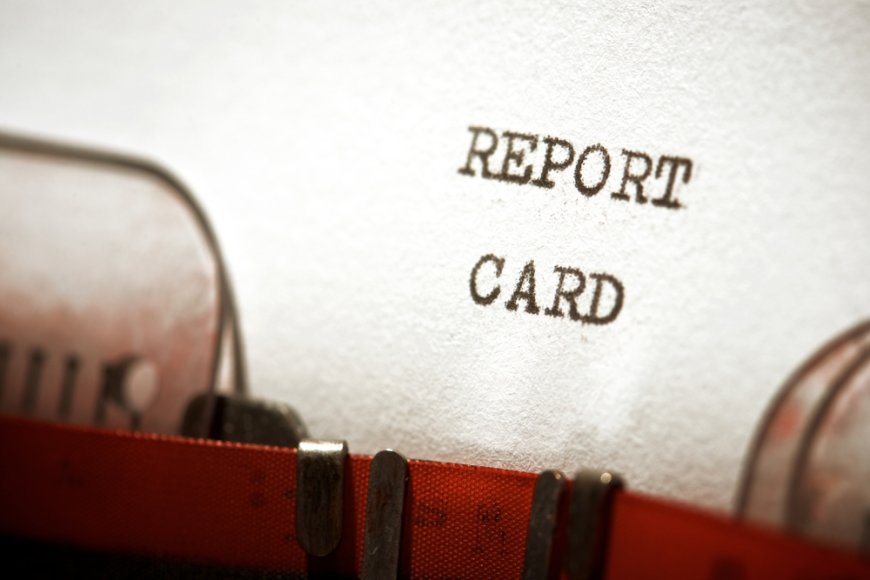


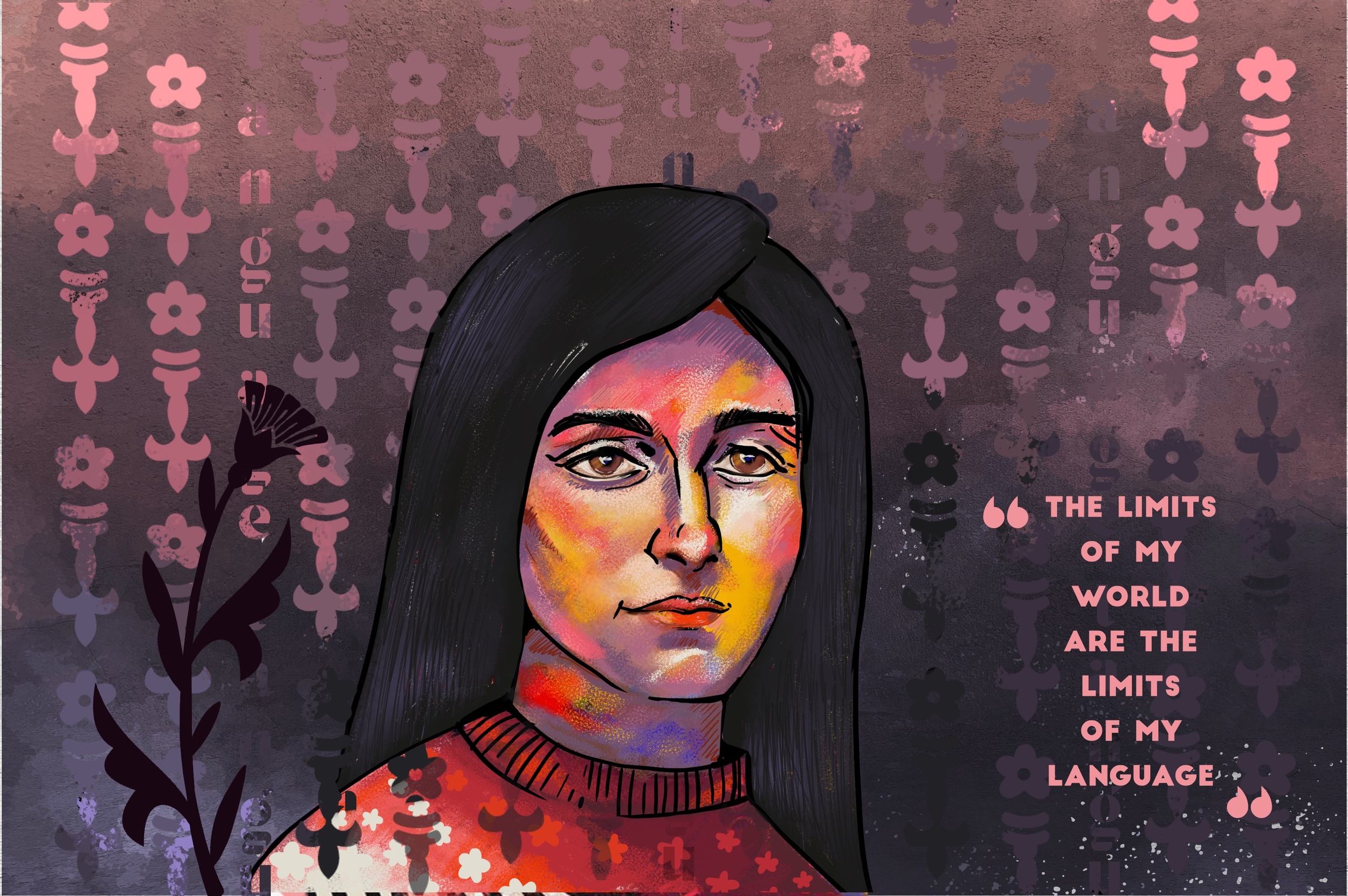



Comments