এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বদৃষ্টিও (worldview) বদলায়, এবং তার সঙ্গে মানবিক শাস্ত্রগুলোর রূপান্তর ঘটে, যা অবধারিতভাবে ইতিহাস ও ইতিহাস-দর্শনের ধারণাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে।
আধুনিক পাশ্চাত্য উদারনৈতিক (liberal) প্যারাডাইমগুলোর বিশেষত্ব হলো এদের কঠোর ভাববাদবিরোধিতা (anti-metaphysical stance) এবং ইতিহাস-বিরোধিতা। তারা ইতিহাসের অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং একটি খাঁটি বৈজ্ঞানিক-ইন্দ্রিয়বাদী (positivist-empirical) দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে — যেমনটা বার্লিন ও বিংশ শতকের পশ্চিমা একাডেমিক সংস্কৃতিতে স্পষ্ট দেখা যায়।
কিন্তু আমার গবেষণায় আমি উপলব্ধি করেছি — ইতিহাস-দর্শন (philosophy of history) ধর্ম ও শিল্পকলার মতোই মানব অস্তিত্বের এক মৌলিক চিন্তা। যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন তারা ইতিহাসের অর্থ, ধারা, ও লক্ষ্য (telos) নিয়ে চিন্তা করবে — কখনো তা স্পষ্টভাবে, কখনো বা অজান্তে।
আধুনিক পশ্চিমা প্যারাডাইমগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো — তারা প্রকাশ্যে ইতিহাস ও অতীতকে অস্বীকার করে, কিন্তু গোপনে আবার “অগ্রগতি” (progress) ও “রৈখিক ইতিহাস”-এর (linear history) বিশ্বাসে আস্থাশীল। তাদের পূর্বসূরি কান্ত (Kant) যেখানে স্পষ্টভাবে ইতিহাসকে অগ্রগতির পথে দেখেছিলেন, সেখানে তারা একই ধারণা গোপনে বহন করেছে।
রৈখিক ইতিহাসের ধারণা বিপজ্জনক, কারণ এটি প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক রূপ, মূল্যবোধ, ও নৈতিক মানদণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে নেয়। যখন ইতিহাসকে সরলরেখায় বিকাশমান হিসেবে দেখা হয় — যেমন কান্ত করেছিলেন — তখন যে কোনো সংস্কৃতি, যা এই মডেলের সঙ্গে খাপ খায় না, সেটিকে অবিলম্বে “অগ্রগতির পথে বাধা” কিংবা “অধম সংস্কৃতি” হিসেবে দেখা হয়। ফলস্বরূপ, এই সংস্কৃতিকে “বিশ্ব-ইতিহাসে” (world-history) অংশগ্রহণের যোগ্য হিসেবেও গণ্য করা হয় না।
বার্লিন ও তাঁর মতো অনেক পশ্চিমা চিন্তাবিদ রাশিয়াকে এভাবেই দেখেছিলেন। কিন্তু স্প্যাংলারীয় (Spenglerian) দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় — এই রৈখিক ইতিহাস-বোধ, সাংস্কৃতিক সার্বজনীনতার (cultural universalism) দাবী এবং পশ্চিমের অহংকার — সবই ইঙ্গিত দেয় যে পশ্চিমা সংস্কৃতি তার সাংস্কৃতিক বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং এখন পতনের মুখোমুখি। এ কারণেই পশ্চিমা উদারনৈতিক চিন্তাবিদ ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা (Francis Fukuyama) ঠান্ডা যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে ঘোষণা করেছিলেন “ইতিহাসের সমাপ্তি” (The End of History)।
কিন্তু বাস্তবে ইতিহাস শেষ হয়নি; বরং এটি একধরনের “বিরতি” বা “স্থগিতাবস্থায়” প্রবেশ করেছে — এক “ইতিহাস-বিরতির যুগে”, যা আমার ভাষায় Pax Americana-নির্মিত সম্মিলিত বিস্মৃতি (collective amnesia)-এর ফল।
আজ যখন আমরা আবার বিশ্ব-ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, তখন ভূরাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা ফুকুয়ামার সেই “ইতিহাসের সমাপ্তি”-তত্ত্বকে ভেঙে দিয়েছে। ইতিহাস ফিরে এসেছে — এবং এর সঙ্গে ফিরে এসেছে ইতিহাস-দর্শনের প্রয়োজনীয়তা। এই “ইতিহাসের প্রত্যাবর্তন”-এর সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জীবিত হচ্ছে সেইসব চিন্তাবিদ, যাদের কাজকে একসময় পশ্চিমা উদারনৈতিক ধারা প্রত্যাখ্যান করেছিল — যেমন স্প্যাংলার, জুলিয়াস এভোলা (Julius Evola) এবং সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদী ঐ ধারার অন্যান্য চিন্তাবিদ।
এই পুনর্জাগরণ পশ্চিমের ভেতরকার ভূরাজনৈতিক, সমাজ-রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক অস্বাভাবিকতার ফল। অনেকেই বর্তমান বিশ্বের পরিবর্তনগুলো ব্যাখ্যা করতে পারছেন না কান্তীয় রৈখিক ইতিহাস-দৃষ্টির মাধ্যমে।
ফলত, এখন পশ্চিম নিজেই সেই প্রশ্নগুলো করছে, যা একসময় রাশিয়ান স্লাভোফাইলরা করেছিল, যেমন:
“আমরা সভ্যতার সিঁড়ির কোন ধাপে আছি? আমরা কি সপ্তদশ ধাপে পৌঁছেছি, নাকি এখনও নবম ধাপে রয়েছি? আমাদের অবস্থান কোথায়, তা জানলে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।”
এবং স্লাভোফাইলদের সেই পুরনো প্রশ্নগুলোও এখন আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে:
“আমাদের ভাগ্য কী হবে? আমরা কোন পথে যাচ্ছি? পশ্চিমা জাতিগুলোর হাতে কি আমরা ধ্বংস হবো? আমরা কি চিরকাল তাদের পিছিয়ে থাকবো, নাকি একসময় তাদের অতিক্রম করবো? আমরা কি তাদের মতো ভালো হবো, নাকি আরও শ্রেষ্ঠ? আমাদের কি তাদের প্রতি কোনো বিশেষ দায়িত্ব আছে? তাদের কি আমাদের প্রতি কোনো দায়িত্ব আছে? আমরা কি সেই ‘মশীহ জাতি’ যারা তাদের রক্ষা করবে, নাকি আমরা অন্ধকার ও বর্বরতার নিবাস, যে নিজেই এক ভয়ংকর শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারবে না?”
এই ধারণাগুলো আজ রুশ জনগণের সম্মিলিত মনস্তত্ত্বে (collective psyche) স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে — আন্তর্জাতিক, ভূরাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ স্তরে রুশ রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডে, অথবা দার্শনিক আলেকজান্ডার দুগিনের (Alexander Dugin) কর্মে, যিনি এক স্বতন্ত্র “রুশ দর্শন” নির্মাণের প্রয়াস নিয়েছেন। এই প্রশ্নগুলোর অবচেতনে প্রকাশও আমরা রুশ শিল্পকলায় দেখতে পাই।
চলচ্চিত্রে, আলেকজান্ডার সোকুরভের (Alexander Sokurov) Russian Ark এই প্রশ্নগুলোকে শুধু গভীরভাবে অনুসন্ধানই করে না, বরং তা রুশ আত্মার এক অনন্য প্রতিফলনও প্রকাশ করে। ছবিটি পুরোপুরি একটানা এক শটে (one take) ধারণ করা হয়েছে — যা আমার বিচারে রুশ আত্মার অসীমতার প্রতীক। স্প্যাংলার একে বলেছিলেন “একটি অন্তহীন সমতল ভূমি” (endless flat plain), এবং বেরদ্যায়েভও (Berdyaev) এই অনুভূতিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন।
বেরদ্যায়েভের মতে, এই “অসীমতা ও বিশালতা”ই রুশ সংস্কৃতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে তাদের ভাবনাগুলোকে সুশৃঙ্খল রূপে প্রকাশ করতে — যেমনটা পশ্চিম করতে পেরেছিল। কিন্তু সময়ের প্রেক্ষাপটে আজ আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, রাশিয়া প্রকৃতপক্ষে “রূপের দুর্বলতা” (weak sense of form) দ্বারা আক্রান্ত ছিল না, যেমন বেরদ্যায়েভ একসময় বলেছিলেন; বরং সংস্কৃতিটি তখনও যথেষ্ট তরুণ ছিল, তার অভিব্যক্তির উপযুক্ত রূপ খুঁজে পায়নি। ইতিহাসের প্রবাহ যতই এগোচ্ছে, এই রূপগুলো ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হচ্ছে।
রুশ ভূমির “অসীমতা, অস্পষ্টতা, অনন্ততা” প্রতিফলিত হয়েছে শিল্পী ইলিয়া গ্লাজুনভের (Ilya Glazunov) কাজেও। তাঁর বিশাল ঐতিহাসিক চিত্রকর্মগুলো — প্রায় দেয়ালচিত্রের মতো — এই ধারণাগুলোর নিখুঁত প্রতিচ্ছবি: আকারে বিশাল, চরিত্রে পরিপূর্ণ, এবং ইতিহাসে বিস্তৃত।
তার বিখ্যাত কাজ Eternal Russia (১৯৮৮)-তে এক ছবিতেই রুশ ইতিহাসের সমগ্র কাহিনি ধারণ করা হয়েছে — পৌত্তলিক অতীত, সাম্রাজ্যিক যুগ, সোভিয়েত বর্তমান, এবং এমনকি এক পোস্ট-সোভিয়েত ভবিষ্যৎ, যেন এক ভবিষ্যদ্বাণী।
অন্যান্য কাজ যেমন The Contributions of the People of the USSR to World Culture and Civilization (১৯৮০) ও Mystery of the 20th Century (১৯৯৯)-তেও একই ধরণের “ইতিহাস-চিত্র” (history-picture) পাওয়া যায় — যেখানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।
রুশ শিল্পের এই ধারাগুলো আলফনস মুচার (Alphonse Mucha) The Slav Epic সিরিজের কাজগুলোর সঙ্গেও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ২০টি বিশাল পেইন্টিংয়ে মুচা স্লাভ জাতির অতীত ও ভবিষ্যৎ চিত্রিত করেছিলেন। শেষ চিত্রকর্ম Apotheosis of the Slavs (১৯২৬)-এ কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই; সময়কাল হিসেবে তিনি লিখেছিলেন কেবল একটি শব্দ — “Future”।
যদি আমরা সংস্কৃতিকে অস্তিত্বগত সত্তা (ontological entity) হিসেবে দেখি — যেমন স্প্যাংলার ও স্লাভোফাইলরা দেখেছিলেন — তবে প্রতিটি সংস্কৃতি তার নিজস্ব “বিশ্ব-অনুভূতি” (world-feeling) দ্বারা পরিপূর্ণ, যা স্প্যাংলার “প্রাইম-সিম্বল” (prime-symbol) নামে অভিহিত করেছিলেন। এই প্রতীক পুরো সংস্কৃতির ভেতর ছড়িয়ে থাকে এবং এর বৈজ্ঞানিক, শিল্প ও রাজনৈতিক রূপকে আকার দেয়।
রাশিয়ার অনন্য ঐতিহাসিক প্রবৃত্তি, তার নিজস্ব ইতিহাস-চেতনা, স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে মুচা ও গ্লাজুনভের কাজে — যেখানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক অবিচ্ছেদ্য সত্তা হিসেবে যুক্ত। এটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে মিলে যায় সুইস দার্শনিক জঁ গেবসার (Jean Gebser)-এর The Ever-Present Origin (১৯৪৯)-এ উপস্থাপিত “নতুন চেতনার কাঠামো” ধারণার সঙ্গে।
গেবসার তাঁর মেটাহিস্টোরিকাল তত্ত্বে বলেছিলেন — ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মানবচেতনায় এক “অখণ্ড” (integral) কাঠামো উদ্ভূত হয়েছে, যার বৈশিষ্ট্য হলো সময়ের ধারণাকে নতুনভাবে উপলব্ধি করা। পুরনো দৃষ্টিভঙ্গিতে সময় ছিল “পরিমাপযোগ্য সম্পর্কের” বিষয়, যা সময়ের প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করেছিল। কিন্তু নতুন কাঠামো সময়কে “অপরিমেয় গুণ” (immeasurable quality) হিসেবে দেখে — কোনো “পরিমাণ” (quantity) হিসেবে নয়।
বেরদ্যায়েভ তাঁর The Meaning of History (১৯৩৬)-এ লিখেছিলেন, মানুষ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে আলাদা করতে অভ্যস্ত, এবং ভবিষ্যৎকে প্রায়ই বাস্তবতার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। কিন্তু যদি আমরা “চিরন্তন বর্তমান” (eternal present)-কে বিবেচনা করি, তাহলে ভবিষ্যৎ অতীতের চেয়ে বাস্তবে বেশি নয়; উভয়ই একত্রে মিলিত। অতীত টিকে থাকে কেবল আমাদের স্মৃতিতে; ভবিষ্যৎ এখনো জন্ম নেয়নি, এবং আমরা নিশ্চিতও হতে পারি না যে তা কখনো জন্ম নেবে। এই চিন্তাতেই রুশ ইতিহাস-চেতনার পরকালীন (eschatological) দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
অনেককে বিস্মিত করে স্লাভোফাইল চিন্তা ও জার্মান অস্তিত্ববাদীদের (existentialists) মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য; স্প্যাংলার ও দানিলেভস্কির ইতিহাস-দর্শনের মিল; দস্তয়েভস্কি ও নীটশের দার্শনিক সংলগ্নতা। এই দুই ভিন্ন ধারার যোগসূত্র কেবল তখনই বোঝা যায়, যখন কেউ “নতুন চেতনার যুগ” (new structure of consciousness) বা “নতুন অক্ষ যুগ” (new axial age)-এর সম্ভাবনা স্বীকার করে।
তাহলে রাশিয়া — অর্থোডক্স স্লাভ বিশ্বসহ — এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি হিসেবে কেবল এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বোঝা সম্ভব, যা ইতিহাস ও সময়কে অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা হিসেবে মেনে নেয় এবং সংস্কৃতিগুলোর অস্তিত্বগত বাস্তবতা স্বীকার করে। আজকের যুগে প্যারাডাইম এক অবমূল্যায়িত শক্তি। প্রতিটি প্যারাডাইমের পেছনে একটি নির্দিষ্ট বিশ্বদৃষ্টি কাজ করে, এবং সেইজন্য কোনো ব্যক্তি, সংস্কৃতি বা জাতিকে তার নিজের প্যারাডাইম থেকে সরানো প্রায় অসম্ভব — কারণ তাতে তাদের গোটা বিশ্বদৃষ্টি বিপন্ন হয়।
অর্থাৎ, বার্লিন যা রাশিয়ায় উপহাস করেছিলেন — ইতিহাসের একটি লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা দিক আছে — সেটিই কিছু জাতি ও ব্যক্তির কাছে তাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস, যা তাদের অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এই ইতিহাস-দৃষ্টিগুলো কখনোই নিরপেক্ষ নয়; এগুলোকে ব্যবহার করা হয়, এমনকি অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করা হয়, নির্দিষ্ট কোনো দর্শন বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে।
আজ আমরা যা দেখছি — যেমন আলেকজান্ডার দুগিন বলেছেন — তা হলো বিভিন্ন “পরকালীন আখ্যানের” (eschatological narratives) ভূরাজনৈতিক পর্যায়ে মোতায়েন। সভ্যতার সংঘর্ষ সবসময়ই শেষ পর্যন্ত হয় “পরকালতত্ত্বের সংঘর্ষ” — এবং আমি যোগ করবো, “ইতিহাস-দর্শনের সংঘর্ষ”ও বটে।
আমার মূল যুক্তি হলো: কোনো জাতি বা সংস্কৃতির নিজের অবচেতন দৃষ্টিভঙ্গি বা ভবিষ্যৎ-দর্শনের প্রতি বিশ্বাসই তাকে সেই ভবিষ্যৎ বাস্তবে রূপ দেওয়ার দিকে চালিত করে। যদিও বার্লিনের মতো চিন্তাবিদরা ইতিহাসের দর্শনগুলোকে অস্বীকার করে, তবু তাঁদের লেখাগুলো গভীরভাবে পড়লে বোঝা যায়, তাঁরাও নিজেদের এক গোপন দৃষ্টিভঙ্গি বহন করেছেন।
আজ যখন ইতিহাস আবার ফিরে এসেছে, এবং আমরা বিশ্ব-ইতিহাসের নতুন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, তখন মানবতার স্বার্থে আমাদের কর্তব্য — বার্লিন ও তাঁর সমমনা চিন্তাবিদদের দর্শনগুলোকে বুঝে ফেলা, এবং তাদের সম্ভাব্য পরিণতি উপলব্ধি করা। আইজাইয়া বার্লিনের ইতিহাসের কল্পনামূলক দর্শনের (speculative philosophy of history) প্রধান সমালোচনা উপস্থাপিত হয় তাঁর বিখ্যাত রচনা Historical Inevitability (১৯৫৫)-তে। সেখানে তিনি এই ধারার বেশ কিছু মৌলিক সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি নির্দেশ করেন—যেমন এর অন্তর্নিহিত নিয়তিবাদ (determinism), ভবিষ্যদ্বাণীমূলক স্বভাব, এবং অধিবিদ্যাগত (metaphysical) অনুমান।
কার্ল পপারের মতোই—যিনি ইতিহাসের দর্শনের আরেক কঠোর সমালোচক—বার্লিনও শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইতিহাস নিজেই একটি ত্রুটিপূর্ণ শাস্ত্র। এবং কম্টের (Auguste Comte) ধাঁচে তিনি যুক্তি দেন যে ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে হবে—একটি “সামাজিক বিজ্ঞান”-এ (social science) রূপান্তর করতে হবে।
বার্লিন ও পপারের মতে, এই “বৈজ্ঞানিকীকরণ” ইতিহাসে অসীম সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে—যেমন একটি “সামাজিক পদার্থবিদ্যা” (social physics) উদ্ভাবনের সম্ভাবনা, যা পাল্টা “সামাজিক প্রকৌশল”-এর (social engineering) পথ সুগম করবে। এই যুক্তি থেকে দেখা যায়, বার্লিন ও পপারের দৃষ্টিতে ইতিহাসের দর্শন বিপজ্জনক—কারণ এটি অধিবিদ্যাগত অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের মতে, মানবিক বিদ্যাগুলো (humanities) ক্রমে একদিন বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালাই হওয়া উচিত।
তবে পপার ও বার্লিনের ধারণাকে বিপজ্জনক করে তুলেছে এদের নৈতিক, ভূরাজনৈতিক এবং সমাজরাজনৈতিক পরিণতি। এই দুই চিন্তক বিশ শতকের পশ্চিমা দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তার যে প্রধান ধারাগুলো গড়ে দিয়েছে, তার কেন্দ্রে ছিলেন। তাই তাঁদের ধারণাগুলো কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতিকে পরিচালিত করে এমন জ্ঞানের ভিত্তি (episteme)-এরই প্রতিফলন। আলেকজান্ডার দুগিন যেমন যুক্তি দিয়েছেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে জর্জ সোরোস তাঁর ফাউন্ডেশনের নাম রেখেছিলেন “Open Society”—যা সরাসরি পপারের বিখ্যাত গ্রন্থ The Open Society and Its Enemies (১৯৪৫)-এর প্রতি এক স্বীকৃতি।
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ধারণা কখনো নিরপেক্ষ নয়; বরং এগুলো হলো অবচেতন শক্তি, যা রাজনীতি ও সমাজে বাস্তব রূপ পেতে পারে। পপার তাঁর লেখায় সরাসরি “piecemeal social engineering”-এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন—একই সঙ্গে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এমন সমস্ত সত্তার ধারণা, যেগুলোকে তিনি অর্গানিক (জৈব) বা অস্তিত্বমূলক (ontological) বলে মনে করেন: যেমন “সংস্কৃতি”, “সভ্যতা”, “জাতি”, “মানুষের আত্মা” বা “সংস্কৃতির চেতনা”। পপার ছিলেন আধুনিক বস্তুবাদী ও বিজ্ঞানবাদী (scientific materialist) চিন্তার এক প্রকৃষ্ট প্রতিনিধি, যার প্রভাবেই আজকের হাইপারমডার্ন বাস্তবতা গঠিত হয়েছে।
তাঁর (এবং সম্ভবত বার্লিনেরও) দৃষ্টিতে মানুষের আত্মা (human soul) হলো এক ভ্রান্ত অধিবিদ্যাগত ধারণা, যা পরিত্যাজ্য—যেমন তাঁরা সংস্কৃতি ও সমষ্টিগত চেতনার ধারণাকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষকে নামিয়ে আনা হয়েছে কেবল এক যান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গিয়ারে—এক এমন ব্যবস্থায়, যা একটি ক্ষুদ্র ক্ষমতাধর শ্রেণির হাতে নিয়ন্ত্রিত, যারা সাধারণ পশ্চিমা মানুষের বাস্তব জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ফলত পশ্চিমা সমাজ রূপান্তরিত হয়েছে এক “আকৃতিহীন ভিড়ে” (formless mass)।
বর্তমান পশ্চিমা উদারপন্থী (liberal) বিশ্বদর্শন এবং তার ইতিহাসবোধ অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও সমস্যাপূর্ণ। এই মতবাদ যত ছড়িয়ে পড়ছে, ততই এটি মানবিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এমনকি “মানব” ও “আত্মা”-র ধারণাকেও প্রত্যাখ্যান করছে।
এই ধারণাগুলোর বাস্তব প্রয়োগ আজ স্পষ্টভাবে দেখা যায় জর্জ সোরোসের “Open Society Foundation”-এর কার্যক্রমে—যা স্পষ্টতই এসব অমানবিক ও প্রতিআধ্যাত্মিক ভাবনার সচেতন রূপায়ণ।
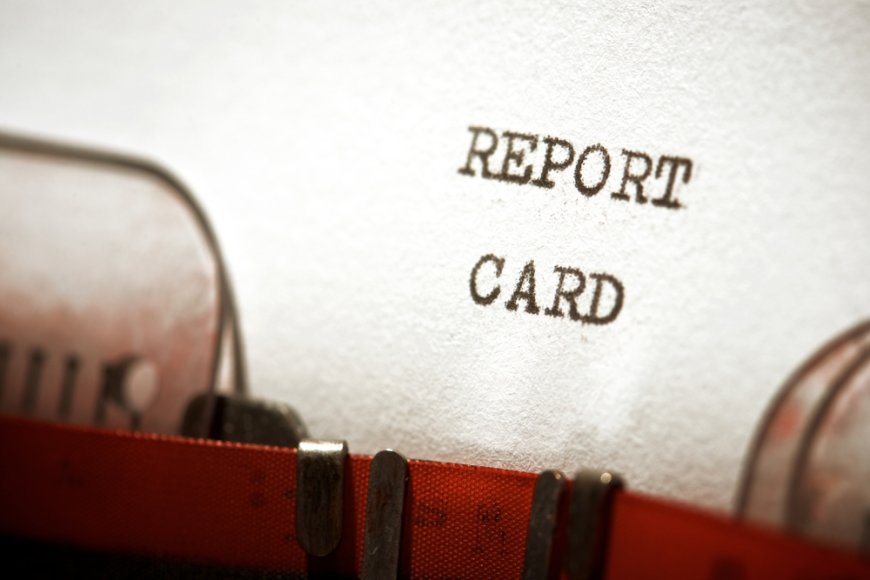


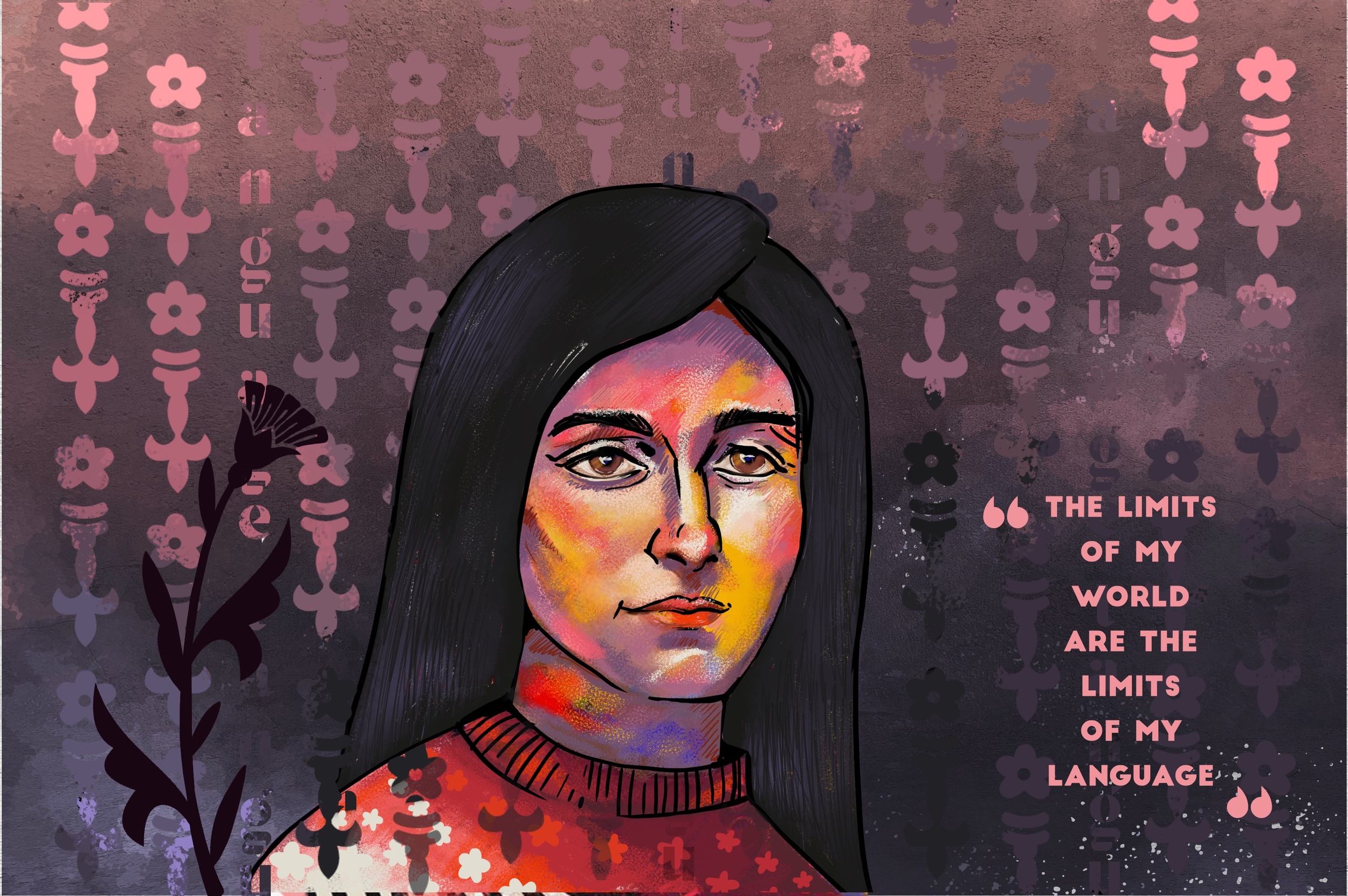


Comments