মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বিমুখিতা
তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সবসময় গণতন্ত্রের পক্ষে থাকবে—এমন নয়। তারা, অন্যদের মতোই, স্বার্থসচেতন শ্রেণি। চীন ও থাইল্যান্ডের মতো দেশে অনেক মধ্যবিত্ত নাগরিক দরিদ্র শ্রেণির পুনর্বণ্টনমূলক দাবিকে ভয় পেয়ে স্বৈরাচারী সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছে—যেখানে রাষ্ট্র তাদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করে। অন্যদিকে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোও যখন মধ্যবিত্তদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়, তখন তারাও অস্থির হয়ে ওঠে।
উদার গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা
আজকের বিশ্বে ন্যূনতম পর্যায়ে হলেও, উদার গণতন্ত্রের বৈধতা নিয়ে এক ধরনের বৈশ্বিক ঐকমত্য গড়ে উঠেছে। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের ভাষায়—
“যদিও গণতন্ত্র এখনো সর্বত্র অনুশীলিত নয় কিংবা সমানভাবে গ্রহণযোগ্যও নয়, তবুও বিশ্বের সাধারণ মতামতের জলবায়ুতে গণতান্ত্রিক শাসন এখন এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে এটি সাধারণত ‘সঠিক’ বলে বিবেচিত হয়।” এই গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সেইসব সমাজে, যেখানে জনগণের বেশিরভাগই নিজেদের মধ্যবিত্ত হিসেবে ভাবতে পারে—অর্থাৎ যেখানে বস্তুগত সমৃদ্ধি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মানুষ কেবল টিকে থাকা নয়, মর্যাদাপূর্ণ জীবনের চিন্তা করতে পারে। এজন্যই উচ্চ উন্নয়ন স্তর ও স্থিতিশীল গণতন্ত্রের মধ্যে সাধারণত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়।
ইসলামি তত্ত্বতন্ত্র ও এর সীমা
কিছু সমাজ—যেমন ইরান ও সৌদি আরব—উদার গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামি তত্ত্বতন্ত্র (theocracy) বেছে নিয়েছে। তবে এই শাসনব্যবস্থাগুলি মূলত বিকাশের ক্ষেত্রে অচল পথ (developmental dead end)।এগুলো কেবলমাত্র টিকে আছে বিশাল তেলসম্পদের ওপর নির্ভর করে। একসময় মনে করা হতো যে, আরব বিশ্ব গণতন্ত্রের “ব্যতিক্রম”—কিন্তু আরব বসন্ত দেখিয়ে দিয়েছে যে, আরব জনগণও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে পারে, যেমনটা পূর্ব ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকায় ঘটেছিল। যদিও তিউনিসিয়া, মিশর বা লিবিয়ায় গণতন্ত্রের যাত্রা কঠিন ও জটিল হবে, তবুও এটি প্রমাণ করেছে—রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কোনো ইউরোপীয় বা আমেরিকান সংস্কৃতির একচ্ছত্র বৈশিষ্ট্য নয়; এটি মানবিক আকাঙ্ক্ষা।
চীনের চ্যালেঞ্জ
উদার গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুতর চ্যালেঞ্জ আজ আসে চীন থেকে—যে দেশ সফলভাবে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও আংশিক মুক্তবাজার অর্থনীতি-কে একত্র করেছে।
চীন দীর্ঘ দুই হাজার বছরের দক্ষ প্রশাসনিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। তারা সোভিয়েত ধাঁচের কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থনীতি থেকে এক উন্মুক্ত, গতিশীল অর্থনীতিতে রূপান্তর ঘটিয়েছে—এবং তা করেছে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে। অনেকেই এখন চীনা ব্যবস্থার প্রশংসা করে—শুধু অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য নয়, বরং জটিল সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণের সক্ষমতার জন্যও। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের নীতি-অচলাবস্থার (policy paralysis) সঙ্গে তুলনা করলে চীনের দ্রুততা বিস্ময়কর। বিশেষ করে ২০০৮–০৯ সালের আর্থিক সংকটের পর, চীনের নেতারাই “চীন মডেল” (China Model) প্রচার করতে শুরু করে—যেন এটি উদার গণতন্ত্রের এক কার্যকর বিকল্প।
চীনা মডেলের সীমাবদ্ধতা
তবে চীনা মডেল সম্ভবত পূর্ব এশিয়ার বাইরের অঞ্চলগুলিতে কখনোই কার্যকর বিকল্প হয়ে উঠবে না।
প্রথমত, এটি সাংস্কৃতিকভাবে বিশেষায়িত একটি মডেল। চীনা সরকার গঠিত হয়েছে বহু শতাব্দীর মেধাভিত্তিক নিয়োগ, প্রশাসনিক পরীক্ষা, শিক্ষার প্রতি উচ্চ মূল্যায়ন, এবং প্রযুক্তিগত কর্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা-র ওপর। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ এই ধরনের ঐতিহ্য বা কাঠামো অনুসরণ করতে পারবে না। যারা আংশিকভাবে পেরেছে—যেমন সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া—তারা মূলত চীনা সংস্কৃতির প্রভাববলয়ে ছিল। চীনারা নিজেরাও সন্দিহান যে এই মডেল রপ্তানি করা সম্ভব কি না। তথাকথিত “বেইজিং কনসেনসাস” আসলে পশ্চিমা বিশ্লেষকদের উদ্ভাবন, চীনের নিজস্ব ধারণা নয়।
দ্বিতীয়ত, এই মডেল টেকসই কি না, তা স্পষ্ট নয়। রপ্তানিনির্ভর প্রবৃদ্ধি ও উপর থেকে নিচে নীতিনির্ধারণ দীর্ঘমেয়াদে ফলপ্রসূ থাকবে—এমন নিশ্চয়তা নেই।
উদাহরণস্বরূপ, ২০১১ সালের ভয়াবহ হাই-স্পিড ট্রেন দুর্ঘটনার পর সরকার উন্মুক্ত তদন্ত ও আলোচনা নিষিদ্ধ করেছিল, এমনকি সংশ্লিষ্ট রেল মন্ত্রণালয়কেও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারেনি। এটি ইঙ্গিত দেয়—চীনা রাষ্ট্রযন্ত্রের ভেতরেও বহু লুকানো দুর্বলতা ও অদক্ষতা রয়েছে, যা কার্যকারিতার মুখোশের আড়ালে চাপা পড়ে আছে।
তৃতীয়ত, চীন একদিন গুরুতর নৈতিক সংকটে পড়বে। রাষ্ট্র তার কর্মকর্তাদের নাগরিকদের মৌলিক মর্যাদা রক্ষার বাধ্যবাধকতা দেয় না। প্রায় প্রতিদিনই জমি দখল, পরিবেশ লঙ্ঘন, কিংবা কর্মকর্তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিবাদ ঘটে। যতদিন প্রবৃদ্ধি দ্রুত, ততদিন এসব চাপা থাকে; কিন্তু প্রবৃদ্ধি থেমে গেলে জমে থাকা ক্ষোভ বিস্ফোরিত হবে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এখনো সমতা-নির্ভর মতবাদের দাবিদার হলেও বাস্তবে সমাজে বৈষম্য ক্রমবর্ধমান—এবং রাষ্ট্রের কোনো নৈতিক ভিত্তি অবশিষ্ট নেই।
চীনের স্থায়িত্বের প্রশ্ন
চীনা ব্যবস্থার স্থিতিশীলতাকে তাই অবধারিত ধরা যায় না। চীনা সরকার দাবি করে যে তাদের জনগণ “সংস্কৃতিগতভাবে আলাদা”—তারা সবসময় “উন্নয়নমুখী স্বৈরতন্ত্রকেই” অগ্রাধিকার দেবে বিশৃঙ্খল গণতন্ত্রের চেয়ে। কিন্তু ইতিহাস বলে, একবার মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিস্তৃত হলে—তারা অন্যত্র যেমন আচরণ করেছে, চীনেও তেমনি আচরণ করবে। অন্য কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলো হয়তো চীনের সফলতা অনুকরণ করার চেষ্টা করবে, কিন্তু ৫০ বছর পর বিশ্বের বেশিরভাগ অঞ্চল চীনের আজকের চেহারার মতো হবে—এমন সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।
গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক পরিবর্তন এবং উদার গণতান্ত্রিক মতাদর্শের আধিপত্যের মধ্যে একটি বিস্তৃত সম্পর্ক বিদ্যমান। বর্তমানে কোনো বিকল্প মতাদর্শ দৃশ্যমান নয়, যা গণতন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। তবুও কিছু উদ্বেগজনক অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রবণতা স্পষ্ট—যেগুলো অব্যাহত থাকলে আধুনিক উদার গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এমনকি গণতান্ত্রিক মতাদর্শের আধিপত্যও প্রশ্নবিদ্ধ হবে।
সমাজবিজ্ঞানী ব্যারিংটন মুর একবার বলেছিলেন:
“No bourgeois, no democracy” — অর্থাৎ, মধ্যবিত্ত শ্রেণি না থাকলে গণতন্ত্রও থাকবে না। মার্কসবাদীরা তাদের “কমিউনিস্ট ইউটোপিয়া” পায়নি, কারণ পরিণত পুঁজিবাদ শ্রমিক সমাজ নয়, মধ্যবিত্ত সমাজ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যদি প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের অগ্রগতি এমন হয় যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভিত্তিই ভেঙে পড়ে—তাহলে উদার গণতন্ত্র কি টিকে থাকবে?
মধ্যবিত্ত শ্রেণির পতন
প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের এমন এক পর্যায় এসেছে যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। এর প্রমাণ ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান— যুক্তরাষ্ট্রে গড় আয় (median income) ১৯৭০-এর দশক থেকে বাস্তব হিসেবে প্রায় স্থবির। এই স্থবিরতার অভিঘাত কিছুটা প্রশমিত হয়েছে কারণ পরিবারের আয়ে এখন দুটি উপার্জনকারী থাকে—পুরুষ ও নারী উভয়েই কাজ করে। কিন্তু এই ভারসাম্য ছিল অস্থায়ী। অর্থনীতিবিদ রঘুরাম রাজনের মতে, আমেরিকা যেহেতু সরাসরি সম্পদ পুনর্বণ্টন (redistribution) করতে রাজনৈতিকভাবে অনিচ্ছুক, তাই গত প্রজন্মে তারা একটি বিপজ্জনক ও অদক্ষ বিকল্প পথ নিয়েছে—নিম্নআয়ের মানুষদের জন্য সহজ ঋণ ও গৃহঋণের (mortgage) প্রণোদনা দেওয়া। চীনসহ অন্যান্য দেশ থেকে সস্তা অর্থপ্রবাহ (liquidity) এই ঋণনীতিকে আরও ত্বরান্বিত করে, ফলে সাধারণ আমেরিকানদের মনে এক প্রকার ভ্রান্ত সমৃদ্ধির অনুভূতি জন্ম নেয়—যেন তাদের জীবনমান ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। কিন্তু ২০০৮–০৯ সালের আবাসনবুদবুদের পতনের (housing bubble burst) মাধ্যমে এই মায়া ভেঙে যায়—এটি ছিল এক নিষ্ঠুর বাস্তবতায় প্রত্যাবর্তন। আজকের আমেরিকানরা হয়তো সস্তা মোবাইল ফোন, পোশাক ও সোশ্যাল মিডিয়া পাচ্ছেন, কিন্তু একইসঙ্গে তারা নিজেদের বাড়ি, স্বাস্থ্যবীমা ও অবসরকালীন নিরাপত্তা—এসব জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছেন।
প্রযুক্তিগত বৈষম্য ও নতুন পুঁজিবাদ
ভেঞ্চার পুঁজিপতি পিটার থিয়েল এবং অর্থনীতিবিদ টাইলার কাউয়েন যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা আরও উদ্বেগজনক। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সুফল আজ অল্পসংখ্যক মেধাবী ও শিক্ষিত মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এই প্রবণতা গত প্রজন্মে যুক্তরাষ্ট্রে বৈষম্যের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ১৯৭৪ সালে দেশের শীর্ষ ১ শতাংশ পরিবার জাতীয় আয়ের ৯ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত; ২০০৭ সালে সেটি বেড়ে হয় ২৩.৫ শতাংশ।
প্রযুক্তি: বন্ধু নাকি শত্রু
বাণিজ্যনীতি ও করনীতি এই বৈষম্যকে কিছুটা ত্বরান্বিত করেছে বটে, কিন্তু আসল দায় প্রযুক্তির। পূর্ববর্তী শিল্পযুগে—যেমন টেক্সটাইল, ইস্পাত বা জ্বালানির যুগে—প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সুফল শ্রমবাজারে কিছুটা হলেও ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু এখনকার “স্মার্ট মেশিনের যুগে” (Shoshana Zuboff-এর ভাষায়) প্রযুক্তি মানুষের শ্রমের বিকল্প হয়ে উঠছে—এমনকি উচ্চদক্ষতার কাজেও। সিলিকন ভ্যালির প্রতিটি সাফল্য মানে অর্থনীতির অন্য প্রান্তে হাজারো নিম্নদক্ষতার চাকরির বিলুপ্তি—এবং এই প্রবণতা এখনো শেষ হয়নি। অতীতে বৈষম্য ছিল স্বাভাবিক—প্রাকৃতিক প্রতিভা বা চরিত্রের পার্থক্যের কারণে। কিন্তু আজকের প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্ব এই পার্থক্যকে অসীমভাবে বাড়িয়ে তুলছে। উদাহরণস্বরূপ, উনিশ শতকের কৃষিনির্ভর সমাজে গণিতজ্ঞ হওয়ার খুব একটা সুযোগ ছিল না; আজ সেই দক্ষতা আপনাকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা অর্থনৈতিক জাদুকরে পরিণত করতে পারে—যার আয় কোটি কোটি ডলার।
বিশ্বায়ন ও চাকরির স্থানান্তর
মধ্যবিত্তের পতনের আরেকটি কারণ হলো বিশ্বায়ন। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যয়ের হ্রাস এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শতকোটি নতুন শ্রমিকের প্রবেশ—এই দুই কারণে উন্নত দেশগুলোর ঐতিহ্যবাহী মধ্যবিত্ত পেশাগুলি এখন অন্যত্র অনেক কম খরচে সম্পন্ন হচ্ছে। অর্থনৈতিক মডেল যেহেতু মোট আয়ের সর্বাধিকীকরণকে (aggregate income maximization) অগ্রাধিকার দেয়, তাই আউটসোর্সিং ছিল প্রায় অবশ্যম্ভাবী। তবে বুদ্ধিদীপ্ত নীতি ও দূরদৃষ্টি কিছু ক্ষতি রোধ করতে পারত। জার্মানি সফলভাবে তার শিল্পভিত্তি ও শ্রমিক শ্রেণির বড় অংশ রক্ষা করেছে, একইসঙ্গে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায়ও টিকে আছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য আনন্দের সঙ্গে নিজেদের “পরিষেবা-ভিত্তিক অর্থনীতি” হিসেবে রূপান্তর করেছে—যেখানে উৎপাদনশিল্পের পতনকে প্রায় উৎসবমুখরভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে। মুক্তবাণিজ্য ধীরে ধীরে তত্ত্ব থেকে মতাদর্শে পরিণত হয়। যখন মার্কিন কংগ্রেস চীনের মুদ্রা-অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিতে চাইল, তখন তাদের অভিযুক্ত করা হলো “সংরক্ষণবাদী” (protectionist) হিসেবে—যেন বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্র ইতিমধ্যেই সমান। “জ্ঞান-অর্থনীতি”-র সৌন্দর্যের গল্প শোনা গেল—যেখানে ময়লা, ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার কাজের জায়গা নেবে সৃজনশীল, উচ্চশিক্ষিত কর্মীরা। কিন্তু এই রোমান্টিক আখ্যান ছিল বাস্তব ডি-ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ওপর এক আবরণ।
নতুন অর্থনীতির সুফল গিয়েছে মূলত অল্প কয়েকজন উচ্চবিত্তের কাছে—অর্থনীতি ও প্রযুক্তিখাতের অভিজাতদের কাছে—যারা গণমাধ্যম ও রাজনীতির কথোপকথনও নিয়ন্ত্রণ করেছে।
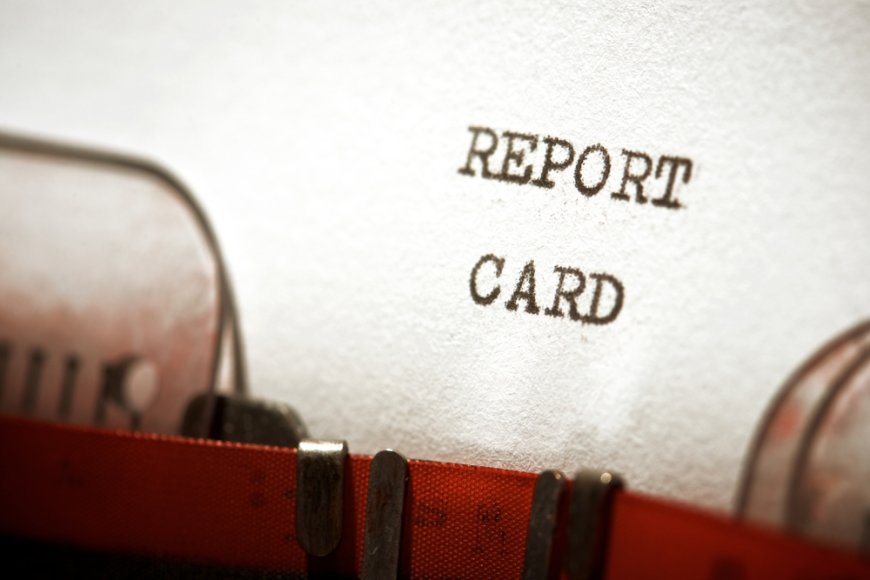


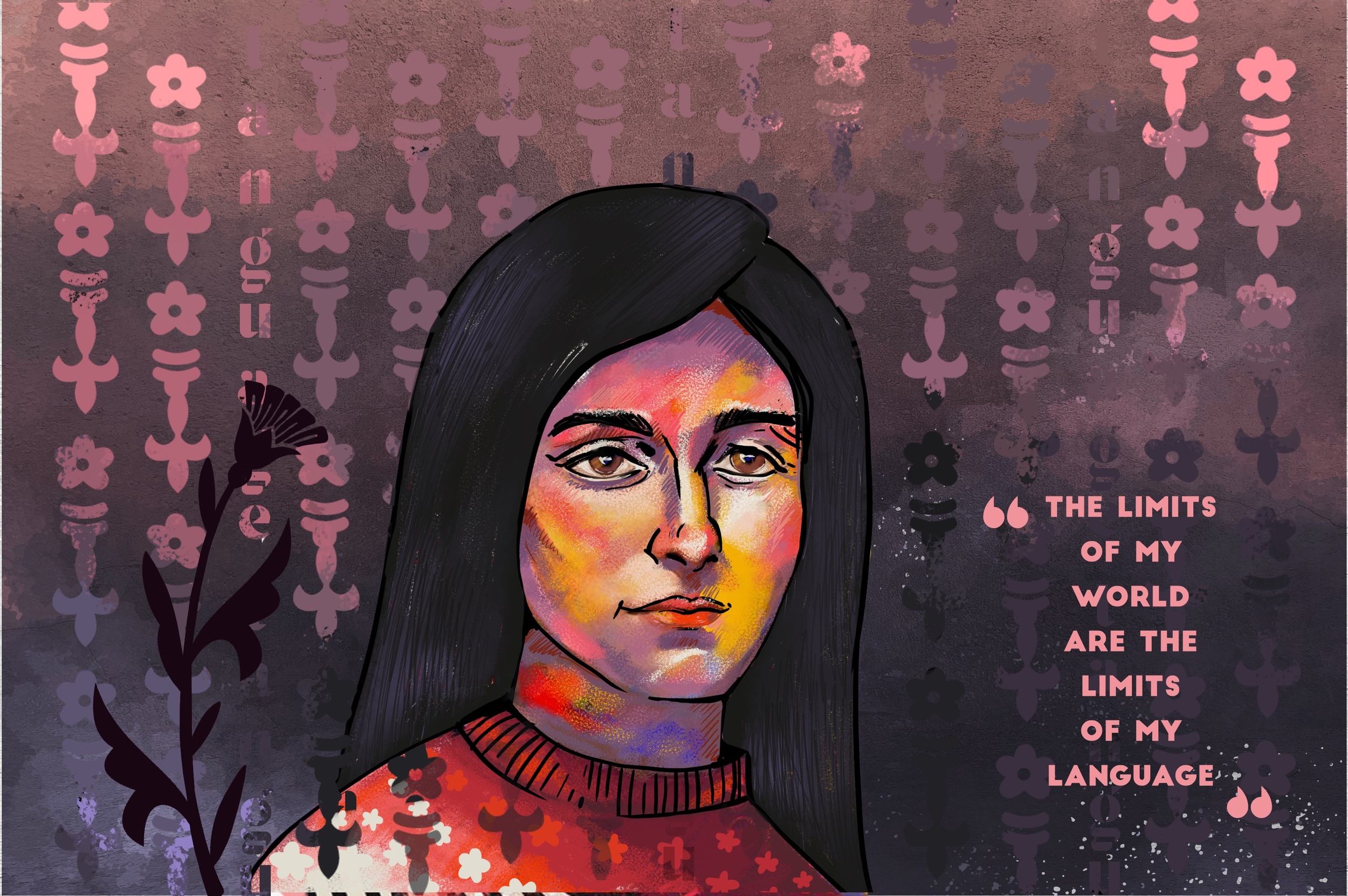



Comments