২০২৫ সালে পৃথিবী এক অদ্ভুত জায়গা। আমরা যে বাতাস শ্বাস নিই, তাতে ভর করে আছে এক ধরনের সাধারণ হতাশা ও অস্থিরতার অনুভূতি। অনেকেই অসুখী। শুধু গরিব, বঞ্চিত বা নিপীড়িত মানুষরাই নয় ; যারা শীর্ষে আছে, তারাও সুখী নয়।
কমেডিয়ান বিল বার একবার বলেছিলেন, বিলিয়নিয়াররাও এক বিলিয়ন ডলার পেয়ে সুখী নয়। কিন্তু বিষয়টি শুধু অর্থের সীমাবদ্ধতায় আটকে নেই। বিশাল ভৌগোলিক আয়তনসমৃদ্ধ দেশগুলো, যেমন রাশিয়া, তারাও তাদের জমির পরিমাণে সন্তুষ্ট নয়। তারা আরও চায়। তারা এমন জমি চায়, যা তাদের নয়।
এবং হয়তো সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো , পৃথিবীর প্রথম অর্থনীতি, ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক শক্তির অধিকারী দেশটি বিশ্বাস করে যে তারা তাদের মহত্ত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এবং তারা তা ফেরত চায়। তারা চায় ‘আমেরিকাকে আবার মহান’ করতে। এভাবেই জন্ম নেয় ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ বা MAGA আন্দোলন, এবং তার নবীস্বরূপ ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প।
আমি বিশ্লেষণ করব ট্রাম্প, ট্রাম্পবাদ (Trumpism), এবং MAGA-এর প্রভাব বিশ্বের বাকি অংশে — অর্থাৎ সেই মানবসমাজে, যারা সবসময় আমেরিকার পরেই স্থান পায়, যদি আমেরিকাকে সবসময় “প্রথমে” রাখা হয়। এখানে আলোচিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ‘অনিচ্ছুক সাম্রাজ্য’ (Reluctant Empire) ধারণা। যেমন গবেষণায় দেখা গেছে , “প্রেটার-ঔপনিবেশিক মন” (praeter-colonial mind) বলতে বোঝায় এমন এক মানসিক কাঠামো, যা চেষ্টা করে আমাদের তথাকথিত “উত্তর-ঔপনিবেশিক” বিশ্বের মধ্যে ঔপনিবেশিকতার নানা উত্তরাধিকারের অর্থ অনুধাবন করতে। ‘Praeter’ উপসর্গের বিভিন্ন অর্থ যেমন ‘অতীত, দ্বারা, অতিক্রম করে, উপরে, অতিরিক্তভাবে, পাশাপাশি’ এই দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা প্রকাশ করে। ফলে, প্রেটার-ঔপনিবেশিক মন একসঙ্গে ঔপনিবেশিকতাকে অতীত ও বর্তমান উভয় হিসেবে দেখে, তার অসংখ্য উত্তরাধিকারের বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে। এটি এমন এক মানসিক অবস্থান, যা ঔপনিবেশিকতার সীমানা ছাড়িয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য নতুন দৃষ্টিকোণ অর্জনের চেষ্টা করে।
এখন, যদি MAGA সত্যিই তার অনুসারীদের বিশ্বাস অনুযায়ী একটি “বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন” (isolationist movement) হতো, তাহলে প্রেটার-ঔপনিবেশিক মনের এ বিষয়ে বলার তেমন কিছুই থাকত না। এটি কেবল একটি অভ্যন্তরীণ আমেরিকান ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হতো, যার বিশ্বব্যাপী কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু MAGA-এর নবী এক ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছেন। উত্তর আমেরিকার ভূমিখণ্ডে অবস্থিত এক “দুর্গ আমেরিকা” বা Fortress America-তে পশ্চাদপসরণ না করে, ট্রাম্প শুরু করেছেন এক নতুন আন্তর্জাতিক অভিযাত্রা । এমন এক প্রচেষ্টা যা শুধু মিত্রতা পুনর্বিন্যাসই নয়, বরং সীমান্ত পুনরায় আঁকারও আহ্বান জানায়। এ রকম প্রচেষ্টা পৃথিবী শেষবার দেখেছিল ১৮৮৪–১৮৮৫ সালের বার্লিন সম্মেলন কিংবা ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তির সময়।
প্রেটার-ঔপনিবেশিক মন আজকের এই পরিবর্তনশীল বিশ্বকে কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে, সেটিই এই আলোচনার মূল বিষয়। তবে তার আগে, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার যা ভবিষ্যৎ আলোচনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।
রূপান্তরের কল্পনা (Transitional Fantasies)
থমাস ম্যাথিউ ক্রুকস (Thomas Matthew Crooks) জন্মগ্রহণ করেন ২০০৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, পেনসিলভানিয়া রাজ্যে। মৃত্যুও হয় সেই একই রাজ্যে, ২০২৪ সালের ১৩ জুলাই, বয়স তখন মাত্র ২০। মৃত্যুর কারণ: এক স্নাইপারের গুলি। তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল, তার নিজের গুলির প্রতিক্রিয়ায় যে গুলি সে ছুঁড়েছিল এক ব্যক্তির দিকে, যিনি তখন বাটলার নামের ছোট্ট শহরে এক জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। যদি সেদিন ক্রুকস তার উদ্দেশ্যে সফল হতো এবং তার নিজের পরিণতি যাই হোক না কেন আজকের পৃথিবী সম্পূর্ণ ভিন্ন হতো। এটি হতো এমন এক পৃথিবী, যেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প থাকতেন না।
নিশ্চয়ই, এমন এক পৃথিবী অনেক বেশি নীরব হতো। যেমন ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে এক সাক্ষাৎকারে লুইজিয়ানার রিপাবলিকান সিনেটর জন কেনেডি মন্তব্য করেছিলেন,
“প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেভাবে আছেন, তিনি জোরেসরে আছেন, এবং তাঁর এই জোরালো উপস্থিতি ইউরোপকে তাদের অর্থনীতি ও জাতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ে জাগিয়ে তুলেছে।” (The Post Millennial, 2025)।
ট্রাম্প সেই হত্যাচেষ্টা থেকে বেঁচে যান, এবং একই বছর তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তিনি এখনো তাঁর আগের মতোই উচ্চকণ্ঠ। তবে এই ঘটনার সবচেয়ে কর্ণবিদারক দিক হলো বিদ্রূপাত্মকভাবে আমরা কত কম কথা বলি সেই তরুণ ছেলেটিকে নিয়ে, যিনি ইতিহাসের গতিপথই বদলে দিতে পারতেন। কত নীরব আমরা ক্রুকসকে নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, সেই সপ্তাহের সংবাদ চক্রের প্রচণ্ড উত্তেজনা কেটে যাওয়ার পর মিডিয়া সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যায়। সেই ভাগ্যবিধ্বস্ত দিনের ওপর আজ পর্যন্ত কোনো বই, প্রামাণ্যচিত্র, বা সিনেমা প্রকাশিত হয়নি— যেদিন এক ট্র্যাজিক জীবন শেষ হয়েছিল। এমনকি যারা আজকের রাজনৈতিক সহিংসতাকে ব্যাখ্যা করতে ক্রমবর্ধমানভাবে “পিছিয়ে পড়া, রাগান্বিত তরুণ পুরুষদের” মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছেন, তারাও টম ক্রুকসের এই করুণ কাহিনিতে আগ্রহ দেখাননি।
এই গল্পটি আমাদের সময়ের অন্ধকার ক্যানভাসের অংশ। এমন এক সময়, যখন শুধু যারা সুখী হওয়ার সব উপাদান রাখে তারা-ই অসুখী নয়, বরং সাধারণ, নীরব মানুষও হঠাৎ তাদের মনে অন্ধকার চিন্তা পোষণ করতে শুরু করে। ট্রাম্প তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম দিকেই যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের ওপর যে নজিরবিহীন রাজনৈতিক ঝড় বইয়ে দেন, তার মুখে অনেক উদার মানবতাবাদী ট্রাম্পের অবসান কল্পনা করতে শুরু করেন। যদি সেটি “দ্বিতীয় সংশোধনী”র (Second Amendment) ভুল প্রয়োগে না হয়— অর্থাৎ ‘অস্ত্র বহনের অধিকার’ তবে হয়তো কেউ কেউ নীরবে চেয়েছেন, বিষয়টি আরও প্রাত্যহিক কোনো পথে হোক; যেমন, হৃদরোগে মৃত্যু বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ।
দুঃখজনক সময় বটে, যদি রাজনৈতিক মতপার্থক্য এমন জায়গায় পৌঁছায় যেখানে সমাধান হিসেবে কেবল আরেকজন মানুষের মৃত্যুর কল্পনাই থাকে।
একটি ট্রাম্পবিহীন বিশ্ব নিঃসন্দেহে কম কোলাহলপূর্ণ হতো। কিন্তু তা কি সত্যিই ভিন্ন হতো? কমেডিয়ান ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার জন স্টুয়ার্ট দেখিয়েছেন, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন উদারপন্থীরা “ফিভার ড্রিম থিওরি” (fever dream theory) তুলে ধরে আসছেন— যেখানে বলা হয়, ট্রাম্প, ট্রাম্পবাদ ও MAGA কোনো মূলধারার অংশ নয়, বরং এটি একটি অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম, যা শতাব্দী-প্রাচীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাময়িক বিভ্রম। একদিন, এই ‘জ্বর’ কেটে যাবে, আর আমেরিকা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। এমনটাই তারা বিশ্বাস করেন।
কিন্তু স্টুয়ার্ট মন্তব্য করেন:
“যদি কেউ ২০০০ সালের পর থেকেই জ্বরে ভুগছে, তবে সেটি জ্বর নয়, সেটিই তার স্বাভাবিক দেহের তাপমাত্রা।” (The Daily Show, 2025, সময় 0:54)।
এটিই মূলত বলেছেন অ্যানি কারনি, হোয়াইট হাউস সংবাদদাতা এবং Mad House বইয়ের লেখক, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে এক সাক্ষাৎকারে: “বেশিরভাগ ডেমোক্র্যাট এবং ভোটার এখন বুঝে ফেলেছেন যে MAGA ট্রাম্পের চেয়েও বড় কিছু। এখানে ফেরার কিছু নেই, কোনো প্রমাণ নেই যে কিছু আবার আগের অবস্থায় ফিরছে।” (The Bulwark, 2025, সময় 13:40)।
আমরা কি এর আগে কখনো মার্কিন ইতিহাসে এমন কিছু দেখেছি?
A Century of Un-American Experiments
যদিও আমেরিকানরা বারবার আত্মনিশ্চিতভাবে বলে থাকে যে তারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশে বাস করে, কিন্তু বাস্তবতা হলো— তারা অনেক দিন ধরেই দিশাহীন, এমনকি কোভিডের আগেও (Galloway 2022)। তারা সংগ্রাম করছে, এবং তাদের অসুস্থতার যেসব প্রতিকার তারা খুঁজে পেয়েছে, সেগুলো সবসময় ভালো নয়।
২০২৫ সালের ট্রাম্প-আমেরিকার এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কিছু বিশ্লেষক ফিরে গেছেন মার্কিন ইতিহাসে— তুলনা টানতে ও সতর্ক করতে, যা আগের প্রজন্ম করতে পারেনি, অন্তত দেরি হওয়ার আগে।
রাজনৈতিক নিপীড়ন ও ‘ডাইনী শিকার’-এর পরিবেশে অনেকে স্বাভাবিকভাবেই স্মরণ করছেন ১৯৫০-এর দশকের ম্যাকার্থিবাদের দিনগুলোকে। তাঁর সর্বশেষ বই Red Scare-এর ভূমিকায় ক্লে রাইজেন (Clay Risen) লিখেছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ:
“আলবেয়ার কামু তাঁর উপন্যাস The Plague-এ লিখেছেন যে ‘প্লেগ জীবাণু কখনও সম্পূর্ণ মারা যায় না বা অদৃশ্য হয় না; এটি বছরের পর বছর আসবাবপত্র, কাপড়চোপড়, ঘর বা আলমারিতে ঘুমিয়ে থাকতে পারে; এবং একসময় আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে।’
ঠিক তেমন কিছু ঘটেছিল ১৯৫০-এর দশকে, এবং বলা যায় ১৯৬০, ৭০-এর দশকেও— এবং আমার বিশ্বাস, আজও সেটির ধারাবাহিকতা চলছে। আজকের আমেরিকান অতিদক্ষিণপন্থার একটি ঐতিহাসিক বংশধারা আছে, এবং তা বুঝতে হলে আমাদের তার শিকড় খুঁজতে হবে Red Scare-এর যুগে। এর উৎপত্তি তখন হয়নি, এবং ট্রাম্পবাদ বা MAGA আন্দোলনও ম্যাকার্থিবাদ বা জন বার্চ সোসাইটির পুনরাবৃত্তি নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি সংযোগরেখা রয়েছে।” (Risen 2025, পৃষ্ঠা xiii)। আরও অনেকে আরও পেছনে তাকিয়ে দেখিয়েছেন, কীভাবে ১৯৩০-এর দশকে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ফ্যাসিবাদের উত্থানের সঙ্গে বর্তমান সময়ের নানা সাদৃশ্য রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো র্যাচেল ম্যাডোর (Rachel Maddow)-এর সাম্প্রতিক বই Prequel: An American Fight Against Fascism (Maddow 2023)।
ম্যাডো সেখানে বিশ্লেষণ করেছেন ১৯৩০-এর দশকে উদ্ভূত এক দেশীয় (homebrewed) ফ্যাসিবাদী প্রবণতার পথচলা— যা বর্তমান সময়ের আমেরিকার রাজনীতির গভীরে তার প্রতিধ্বনি রেখে গেছে। ১৯৪০-এর দশকে, এই আন্দোলনের অগ্রযাত্রা ঘটে আংশিকভাবে মূল ‘আমেরিকা ফার্স্ট কমিটি’র (America First Committee) মাধ্যমে — একটি রাজনৈতিক সংগঠন, যা ১৯৪১ সালের ২৩ মে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে এক বিশাল সমাবেশ আয়োজন করে, যার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাইরে রাখা (Ibid, 217)। তবে পার্ল হারবার হামলার পর এই কমিটি ভেঙে যায় (Ibid, 247)।
তখনকার আমেরিকায় তথাকথিত ‘সিলভার শার্টস’ (Silver Shirts) (Ibid, 60) ছাড়া আর কোনো বড় আধা-সামরিক বাহিনী বা ‘প্রিটোরিয়ান গার্ড’ গঠিত হয়নি — যা সাধারণত ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থায় দেখা যায়, যেখানে সেনাবাহিনীর আনুগত্য নিশ্চিত করতে নেতার চারপাশে ব্যক্তিগত বাহিনী তৈরি করা হয়। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এমন কিছু আমেরিকায় কখনো ঘটতে পারে না — ট্রাম্পের ঘনঘন ন্যাশনাল গার্ড ব্যবহারের নজির, বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায়, আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়। ম্যাডো তাঁর সুবিস্তৃত গবেষণার শেষে পাঠককে আহ্বান জানিয়ে বলেন:
“যদি আমরা সাহস করে আমেরিকান ইতিহাসে ফ্যাসিবাদের দিকে গভীরভাবে তাকাই, তাহলে সত্যিটা হলো— আমাদের এই বন্য, অনিশ্চিত একবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস অতীতের প্রতিধ্বনি নয়, বরং তার প্রিকুয়েল (পূর্বসূত্র)।” (Ibid, 309)
তেমনি, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মারসি শোর, টিমোথি স্নাইডার, এবং জেসন স্ট্যানলি ২০২৫ সালে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করে ট্রাম্প-আমেরিকায় ফ্যাসিবাদের আগমনকে নিন্দা জানান, এবং পরবর্তীতে দেশ ত্যাগ করে কানাডায় চলে যান (Shore, Snyder and Stanley 2025)। এখন, যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে চলা ঘটনাগুলিকে বোঝার ক্ষেত্রে ‘রেড স্কেয়ার’ বা ‘ফ্যাসিবাদী’ দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে কার্যকর বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো, তবে আমি মনে করি— আমেরিকার ইতিহাসে এমন আরও একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত আছে, যা সম্ভবত আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে কীভাবে MAGA আন্দোলনের জন্ম হলো, এটি কতদিন টিকে থাকতে পারে, এবং এর প্রভাব কতদূর যেতে পারে। এটি আমেরিকান সমাজের এক অনন্য ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, যা বৃহত্তর অর্থে ‘আমেরিকান এক্সপেরিমেন্ট’-এর অংশ। কেউ কেউ একে বলেন ‘The Noble Experiment’, তবে অধিকাংশ মানুষ চেনে এটি ‘Prohibition’ নামে— অর্থাৎ ১৯২০ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে মদ নিষিদ্ধ করার জাতীয় আইন।
এই বিশেষ অধ্যায়টি নিয়ে ড্যানিয়েল ওক্রেন্ট (Daniel Okrent)-এর বিখ্যাত গবেষণা Last Call: The Rise and Fall of Prohibition (যা পরবর্তীতে কেন বার্নসের প্রামাণ্যচিত্র সিরিজের অনুপ্রেরণাও হয়) ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, কীভাবে আপাতদৃষ্টিতে এতটা “অন-আমেরিকান” এক ঘটনা পৃথিবীর অন্যতম স্বাধীনতাপ্রিয় দেশে সম্ভব হয়েছিল।
ওক্রেন্ট লিখেছেন:
“বাস্তবে, আমেরিকানদের কাছে ছিল কয়েক দশকের সতর্কবার্তা, সেই কয়েক দশক জুড়ে এক অভূতপূর্ব গণআন্দোলন— নৈতিকতাবাদী ও প্রগতিশীলদের, নারী ভোটাধিকারের দাবিদার ও বিদেশিবিদ্বেষীদের এক বিশাল জোট— সংবিধানকে আইনি উপায়ে কব্জা করেছিল, সেটিকে এক নতুন উদ্দেশ্যে বাঁকিয়ে নিয়েছিল।” (Okrent 2010, 1)
প্রকৃতপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ১৮তম সংশোধনী (যা মদ নিষিদ্ধকরণের সাংবিধানিক ভিত্তি তৈরি করে, এবং এর সহগামী আইন Volstead Act) ১৯১৯ সালে চালু হলেও, এর রাজনৈতিক শিকড় ১৮৭০-এর দশক পর্যন্ত প্রসারিত।
To Be Continued..............................
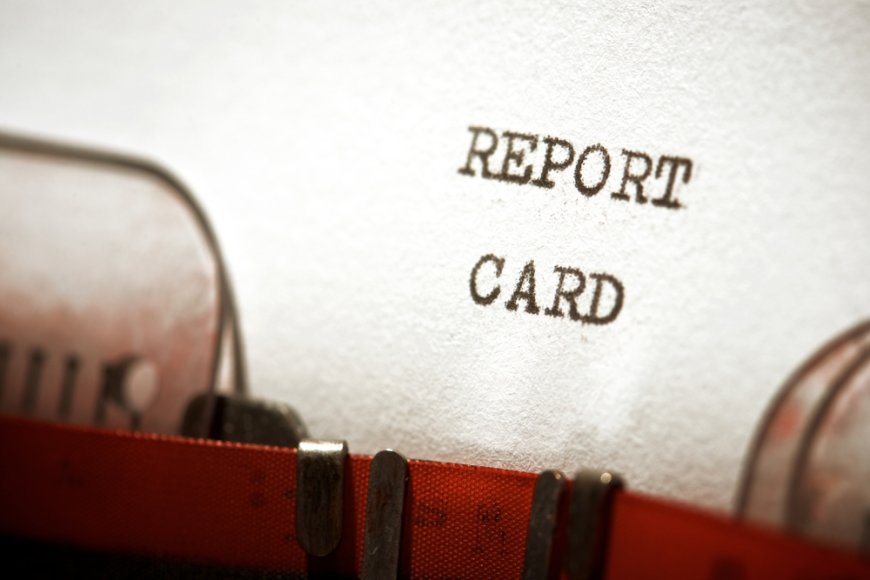


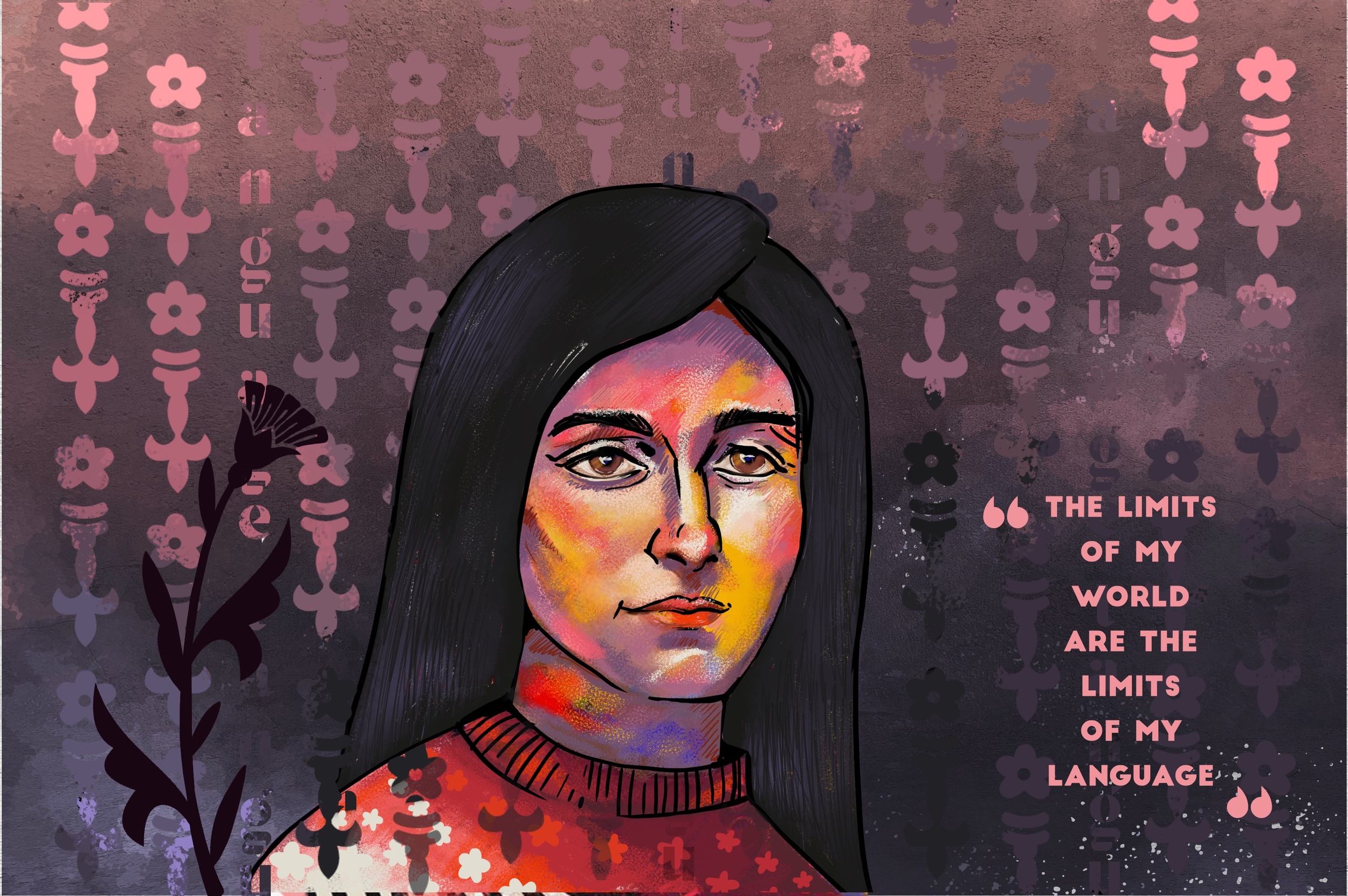


Comments