স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের "ওয়ান সোল অ্যাট এ টাইম: পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল রিফর্ম" প্রবন্ধটি রাজনৈতিক বিজ্ঞানকে একটি একাডেমিক শৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক সংস্কারের বাহন উভয় হিসেবে দেখা যায় এবং এর ভূমিকা নিয়ে একটি চিন্তাশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক নিয়ে আলোচনা করে। ১৯৮৭ সালে আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের ৮৩তম বার্ষিক সভায় তার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেওয়া এই ভাষণটি রাজনৈতিক বিজ্ঞানকে একটি বৃহত্তর নৈতিক, ঐতিহাসিক এবং ব্যবহারিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে। হান্টিংটন অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান এবং নৈতিক দায়িত্ববোধের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য একটি ক্রমবর্ধমানতাবাদী পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি দেন। এই প্রবন্ধটি হান্টিংটনের প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ের একটি সমালোচনামূলক এবং ব্যাপক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। এটি তার কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য, মূল বিষয়, দার্শনিক ভিত্তি, ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত এবং সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা অন্বেষণ করে, একই সাথে বিপরীত যুক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনার সাথে জড়িত। শেষ পর্যন্ত, এই প্রবন্ধটি প্রমাণ করতে চায় যে হান্টিংটনের রাজনৈতিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি—নৈতিক, অভিজ্ঞতাবাদী এবং সংস্কারমূলক—আধুনিক গণতান্ত্রিক অনুশীলন এবং একাডেমিক আলোচনার জন্য গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে।
ভূমিকা
মতাদর্শিক মেরুকরণ, কর্তৃত্ববাদী পুনরুত্থান এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জনগণের আস্থা হ্রাসের এই যুগে, রাজনৈতিক সংস্কারের সাথে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত; এই প্রশ্নটি কেবল একাডেমিক নয় বরং এটি রাজনৈতিক সমাজের অস্তিত্বের প্রশ্ন। বিশেষ করে বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। হান্টিংটন গণতন্ত্রায়ন এবং রাজনৈতিক সংস্কারকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের ভূমিকার জন্য একটি সূক্ষ্ম যুক্তি উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে বিপ্লবী উত্থানের মাধ্যমে নয়, বরং রাজনৈতিক জটিলতা সম্পর্কে নম্রতা ও সচেতনতার সাথে অনুসরণ করাই যেকোনো রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর।
I. একটি নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শৃঙ্খলা হিসেবে রাজনৈতিক বিজ্ঞান
রাজনৈতিক বিজ্ঞানীরা, সাধারণভাবে যেকোনো সমাজকে "ভালো করতে" চান। এই উক্তিটি আদর্শিক উদ্বেগের ডোমেইনে তিনিই সর্বপ্রথম স্থাপন করেন। হান্টিংটনের মতে, রাজনৈতিক বিজ্ঞান কেবল রাজনৈতিক ব্যবস্থার বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের সাথে সম্পর্কিত একটি বুদ্ধিবৃত্তিক অন্বেষণ নয়; এটি ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং দায়িত্বশীল শাসনের মতো লক্ষ্য দ্বারা চালিত একটি নৈতিক উদ্যোগও। হান্টিংটন স্বীকার করেন যে রাজনৈতিক বিজ্ঞানীরা সর্বদা এই লক্ষ্য অর্জনে সফল নাও হতে পারেন, তবে রাজনৈতিক জ্ঞানকে জনকল্যাণের সাথে যুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা তাদের পেশাগত পরিচয়ের অন্তর্গত।
সামাজিক বিজ্ঞান এবং রাজনীতিতে নৈতিক সচেতনতা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদান। হিরশম্যান যেমন ইঙ্গিত করেন, পণ্ডিতদের যদি অর্থবহ এবং নৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কাজ তৈরি করতে হয় তবে তাদের অবশ্যই "নৈতিকভাবে জীবন্ত" এবং নৈতিক উদ্বেগের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। হান্টিংটন এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যুক্তি দেন যে রাজনৈতিক জ্ঞানের সম্প্রসারণ নিজেই শেষ হওয়া উচিত নয়; বরং, এটিকে বৃহত্তর সামাজিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে হবে। এই অবস্থান রাজনৈতিক সত্ত্বাকে একটি কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে যা নিরপেক্ষতাকে ছাড়িয়ে যায় এবং নৈতিকভাবে সম্পৃক্ত হতে আহ্বান জানায়।
এই নৈতিক দৃষ্টিকোণটি কিছু পণ্ডিত যাকে "নিয়মনিষ্ঠ রাজনৈতিক বিজ্ঞান" বলে। তাদের মতে এই বিজ্ঞান শৃঙ্খলার এমন একটি শাখা যা স্পষ্টভাবে মূল্যবোধ, ন্যায়বিচার এবং একটি ভালো সমাজের প্রশ্নগুলোর সাথে জড়িত তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। হান্টিংটনের জন্য, রাজনৈতিক বিজ্ঞানকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তিতেই নয়, নৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতিতে এর অবদানের দ্বারাও মূল্যায়ন করতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক কঠোরতা এবং নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতা তার প্রবন্ধে একটি পুনরাবৃত্তিমূলক মোটিফ এবং এর সবচেয়ে স্থায়ী অন্তর্দৃষ্টিগুলোর মধ্যে একটি গঠন করে।
II. ঐতিহাসিক ভিত্তি: রাজনৈতিক বিজ্ঞানের প্রগতিশীল উৎস
রাজনৈতিক বিজ্ঞানের নৈতিক অভিমুখ সম্পর্কে তার দাবিকে সমর্থন করার জন্য, হান্টিংটন বিশেষ করে আমেরিকান প্রেক্ষাপটে সমাজের বিকাশের একটি ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান করেন। তিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রগতিশীল যুগে এর উৎস খুঁজে পান, যখন উড্রো উইলসন, ফ্র্যাঙ্ক গুডনাউ এর মতো বুদ্ধিজীবীরা অভিজ্ঞতামূলক গবেষণা এবং জনসেবার মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। এই প্রাথমিক রাজনৈতিক বিজ্ঞানীরা বিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষক ছিলেন না; তারা সামাজিক ন্যায়বিচার, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।
হান্টিংটন তুলে ধরেন, কিভাবে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতারা বৃহত্তর প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল শিল্প পুঁজিবাদের বাড়াবাড়ি দমন করা, দুর্নীতি কমানো এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। রাজনৈতিক বিজ্ঞান এবং সংস্কারের মধ্যে এই ঐতিহাসিক যোগসূত্র তার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুকে তুলে ধরে: তিনি বলেন সমাজের এই অংশটি সহজাতভাবে সংস্কারমূলক, এর অনুশীলনকারীদের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা গঠিত।
এছাড়াও তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানি এবং ইতালির মতো কর্তৃত্ববাদী প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের অনুপস্থিতির সাথে আমেরিকান অভিজ্ঞতার বৈপরীত্য তুলে ধরেন। তিনি যুক্তি দেন যে এই দেশগুলোতে রাজনৈতিক বিজ্ঞান বিকশিত হয়নি কারণ অংশগ্রহণ, বহুত্ববাদ বা উন্মুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো স্থান সেখানে ছিল না যা গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক অনুসন্ধানের উভয়ের জন্যই অপরিহার্য শর্ত। সুতরাং, তিনি গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক বিজ্ঞানের মধ্যে একটি মিথোজীবী সম্পর্ক স্থাপন করেন যা উভয়ই একসাথে উন্নতি লাভ করে এবং একটির পতন প্রায়শই অন্যটির দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়।
III. বিপ্লবী রাজনীতির সমালোচনা
হান্টিংটনের প্রবন্ধের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকগুলোর মধ্যে একটি হলো বিপ্লবী রাজনীতি এবং তার সমালোচনা। যুদ্ধ, স্বৈরাচার, অবিচার বা বর্ণবাদ বিলোপের ক্ষেত্রেই হোক না কেন, হান্টিংটন যুক্তি দেন যে নির্মাণের পরিকল্পনা ছাড়াই কেবল ধ্বংসের উপর মনোযোগ দেওয়া নৈতিক ও কৌশলগত উভয় দিক থেকেই ত্রুটিপূর্ণ।
বিপ্লবী আন্দোলনের বিপদ চিত্রিত করতে হান্টিংটন ঐতিহাসিক উদাহরণ ব্যবহার করেন। তিনি কিউবা, ভিয়েতনাম, ইরান এবং কম্বোডিয়াকে এমন ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন যেখানে বিপ্লব তাদের প্রতিস্থাপিত শাসকদের চেয়েও বেশি দমনমূলক শাসনের দিকে পরিচালিত করেছে। তিনি ওয়ালেসা, বেনিগনো একুইনাএবং বুথেলেজি এর মতো রাজনৈতিক সংস্কারকদের কথাও উল্লেখ করেন, যারা শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। এই উদাহরণগুলো আমূল পরিবর্তনের পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান, আলোচনার মাধ্যমে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর তার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে।
এই দৃষ্টিকোণ হান্টিংটনের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। তিনি বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো স্বীকার করেন কিন্তু যারা মনে করেন তারা রাতারাতি সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারবেন তাদের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সতর্ক করেন। তার জন্য, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জটিলতা বোঝা, আপস স্বীকার করা এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করার মধ্যে নিহিত। লক্ষ্য ইউটোপিয়া অর্জন করা নয়, বরং বাস্তববাদী, ধাপে ধাপে পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থবহ উন্নতি করা।
<img src ='https://cms.thepapyrusbd.com/public/storage/inside-article-image/z8dvcso6j.jpeg'>
IV. গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানের আন্তঃনির্ভরশীলতা
হান্টিংটন গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক অন্বেষণ করে তার যুক্তিকে আরও গভীর করেন। গণতন্ত্র যেমন রাজনৈতিক বিজ্ঞানকে বিকশিত হতে সাহায্য করে, তেমনি রাজনৈতিক বিজ্ঞানও গণতন্ত্রের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতায় অবদান রাখতে পারে। জার্মানি, ইতালি ও ব্রাজিলের মতো কর্তৃত্ববাদী-পরবর্তী সমাজে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের সম্প্রসারণের আলোচনা করে তিনি এই বিষয়টি তুলে ধরেন, যেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উত্থান একাডেমিক অনুসন্ধান ও নীতিগত পরামর্শের জন্য স্থান তৈরি করে।
হান্টিংটন রাজনৈতিক বিজ্ঞানের উত্থান এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সম্প্রসারণের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। কম অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতার জন্য কোনো প্রতিযোগিতা না থাকা সমাজে, রাজনৈতিক বিজ্ঞানীদের অধ্যয়নের সুযোগ খুব কমই থাকে। বিপরীতভাবে, উন্মুক্ত, বহুত্ববাদী সমাজে, রাজনীতি অধ্যয়ন শাসনব্যবস্থা বোঝা এবং উন্নত করার জন্য একটি অত্যাবশ্যক হাতিয়ারে পরিণত হয়। তিনি গণতান্ত্রিক উত্তরণে রাজনৈতিক বিজ্ঞানীদের ভূমিকা বাজার অর্থনীতির অর্থনীতিবিদদের ভূমিকার সাথে তুলনা করেন।
এই যুক্তির আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রায়ন প্রচেষ্টার জন্য উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। এটি সুপারিশ করে যে রাজনৈতিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণাকে উৎসাহিত করা গণতন্ত্র প্রসারের একটি মূল্যবান উপাদান হতে পারে। রাজনৈতিক বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে, সমাজ এমন পেশাদারদের একটি গোষ্ঠী তৈরি করতে পারে যারা প্রতিষ্ঠান বিশ্লেষণ করতে, নীতিনির্ধারকদের পরামর্শ দিতে এবং জনবিতর্কে অবদান রাখতে সক্ষম। এই অর্থে, রাজনৈতিক বিজ্ঞান গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি পণ্য এবং প্রচারক উভয়ই হয়ে ওঠে।
V. রাজনৈতিক বিজ্ঞান এবং গণতন্ত্রায়ন: কেস স্টাডি
রাজনৈতিক সংস্কারে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অবদান তুলে ধরতে হান্টিংটন তিনটি দেশের উদাহরণ উপস্থাপন করেন। দেশ তিনটিঃ ব্রাজিল, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রতিটি কেইস রাজনৈতিক বিজ্ঞান, গণতন্ত্রায়ন এবং সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে।
ব্রাজিল: ক্রমবর্ধমান গণতন্ত্রায়ন
ব্রাজিলের ক্ষেত্রে, হান্টিংটন সামরিক অভিজাতদের দ্বারা পরিচালিত সামরিক একনায়কতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের বর্ণনা করেছেন। এই প্রক্রিয়াটি "অস্পষ্ট ক্রমবর্ধমানতা" দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল, যেখানে মেরুকরণ এবং অস্থিরতা এড়াতে পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে এবং প্রায়শই অস্পষ্টভাবে প্রবর্তন করা হয়েছিল। হান্টিংটন উল্লেখ করেছেন যে উত্তরণের মূল ব্যক্তিত্বরা রাজনৈতিক বিজ্ঞান গবেষণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ব্রাজিলিয়ান রাজনৈতিক বিজ্ঞানীরা—যাদের মধ্যে অনেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষিত ছিলেন—সংস্কারের আলোচনাকে রূপ দিতে ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই উদাহরণটি তার প্রতিপাদ্যকে সমর্থন করে যে রাজনৈতিক বিজ্ঞান বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জাম সরবরাহ করে এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তনকে উৎসাহিত করে গণতন্ত্রায়নে অবদান রাখতে পারে।
চীন: রাজনৈতিক বিজ্ঞান একটি হুমকি এবং সুযোগ হিসেবে
চীন একটি আরো জটিল কেস উপস্থাপন করে। হান্টিংটন পর্যবেক্ষণ করেছেন যে শাসনের কর্তৃত্ববাদী প্রকৃতির কারণে চীনে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের বিকাশ সীমিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিজ্ঞান বিভাগগুলো অনুন্নত, এবং রাজনীতির অধ্যয়ন প্রায়শই বিদেশী ব্যবস্থা বা প্রশাসনিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে, চীনা সরকার রাজনৈতিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠানো শুরু করেছে, যা এই শিক্ষার্থীরা কিভাবে কর্তৃত্ববাদী শাসনের বাস্তবতার সাথে গণতান্ত্রিক ধারণাগুলোর সমন্বয় করবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। হান্টিংটন অনুমান করেন যে শাসন একটি দ্বিধাদ্বন্দ্বের মুখোমুখি হবে: হয় এই পণ্ডিতদের স্বীকৃতি দেবে, না হয় তাদের প্রভাব দমন করবে। উভয় ক্ষেত্রেই, রাজনৈতিক বিজ্ঞানের বৃদ্ধি কর্তৃত্ববাদী নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করে এবং ভবিষ্যতের সংস্কারের পথ প্রশস্ত করতে পারে।
দক্ষিণ আফ্রিকা: ডারবান ইন্ডাবা
অবশেষে, হান্টিংটন দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান ইন্ডাবা নিয়ে আলোচনা করেন—একটি সাংবিধানিক সম্মেলন যা নাটাল প্রদেশের গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য একটি কাঠামো নিয়ে আলোচনার জন্য বিভিন্ন জাতিগত ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের একত্রিত করেছিল। তিনি এই প্রচেষ্টাকে ১৭৮৭ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক সম্মেলনের সাথে তুলনা করেন, আপস, সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং অবহিত আলোচনার উপর এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। যদিও ডারবান সংবিধানের সীমিত প্রভাব ছিল, হান্টিংটন এটিকে গভীরভাবে বিভক্ত সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রসারে রাজনৈতিক বিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক রাজনীতির একত্রীকরণের একটি আশাব্যঞ্জক উদাহরণ হিসেবে দেখেন।
VI. ক্রমবর্ধমান সংস্কারের দর্শন
"রাষ্ট্র একটি আত্মা" এই বাক্যটি হান্টিংটনের সংস্কারের দর্শনকে ধারণ করে। এটি ক্রমশঃ, ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং বাস্তবসম্মত প্রত্যাশার প্রতি অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। তিনি যুক্তি দেন, রাজনৈতিক পরিবর্তন ব্যাপক রূপান্তর বা জাঁকজমকপূর্ণ নকশার মাধ্যমে অর্জিত হয় না। পরিবর্তে, এটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কর্মরত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তিদের ধৈর্যশীল কাজের ফল।
এই দর্শন নৈতিক ও অভিজ্ঞতাবাদী উভয় বিবেচনার উপর ভিত্তি করে গঠিত। নৈতিকভাবে, এটি ব্যক্তিদের মর্যাদা এবং জবরদস্তির পরিবর্তে প্ররোচনার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়। অভিজ্ঞতাবাদীভাবে, এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার জটিলতা এবং আমূল পরিবর্তনের অপ্রত্যাশিত পরিণতি স্বীকার করে। হান্টিংটনের জন্য, রাজনৈতিক বিজ্ঞানের ভূমিকা ইউটোপিয়া তৈরি করা নয়, বরং রাজনৈতিক জীবনের উন্নতিতে ধীরে ধীরে অবদান রাখা।
এই পদ্ধতি এডমন্ড বার্ক, রেইনহোল্ড নিবুহর এবং মাইকেল ওকশটের মতো চিন্তাবিদদের প্রচারিত রাজনৈতিক মধ্যপন্থা রীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এটি জননীতিতে "আলোচনামূলক গণতন্ত্র" এবং "ক্রমবর্ধমানতা"র সমসাময়িক তত্ত্বগুলোর সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। আলোচনা, আপস এবং ধারাবাহিকতার উপর জোর দিয়ে হান্টিংটন প্রযুক্তিগত যুক্তিবাদ এবং বিপ্লবী রোমান্টিকতা উভয়েরই একটি বিপরীত চিত্র তুলে ধরেন।
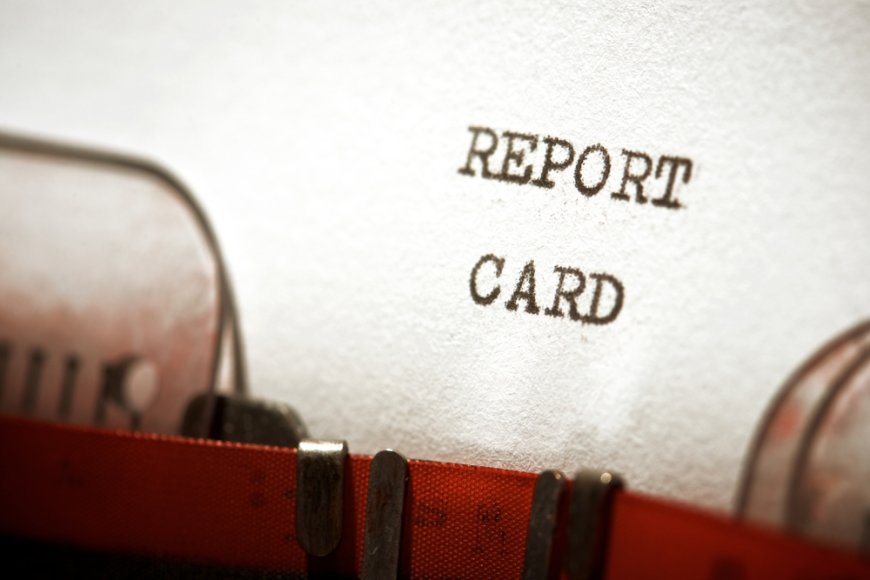


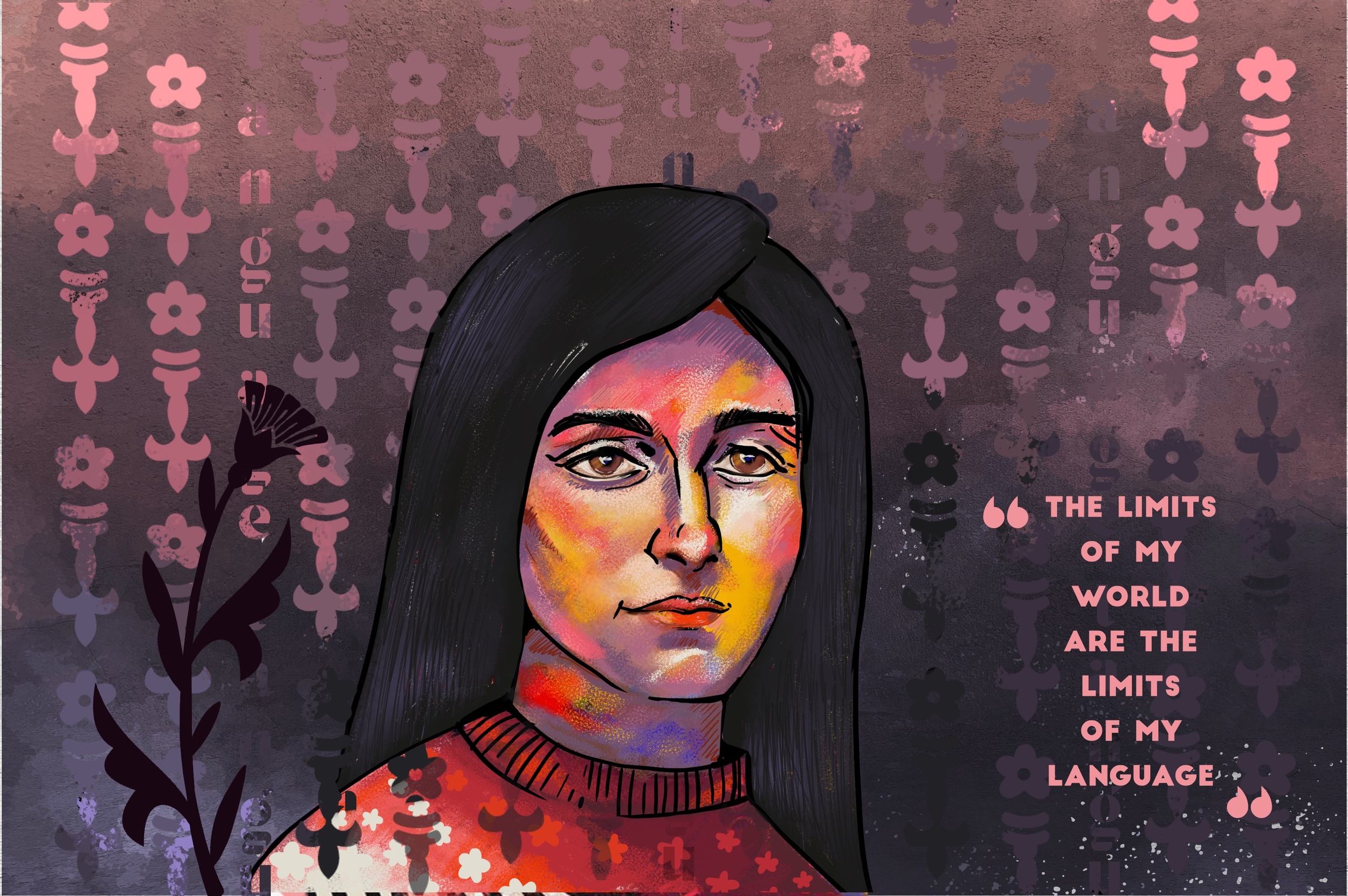



Comments