২০০১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, এসসিও (SCO) বিশেষ প্রভাবশালী কোনো উদ্যোগ হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। অনেকটা ব্রিকসের মতোই, এর বৈঠকগুলো আমার কাছে সবসময় এমন এক “ক্ষুব্ধ শক্তিধরদের অক্ষ”–এর আড্ডাখানা মনে হতো, যেখানে তারা প্রতীকীভাবে মার্কিন নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার স্তম্ভগুলো দুর্বল করার চেষ্টা করে। কিন্তু এ বছর দৃশ্যপট কিছুটা ভিন্ন ছিল: চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কাছে টানার ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি হয়েছে—যা ছিল অন্তত প্রতীকী, যদি বাস্তব না-ও হয়। এর বিশেষত্ব হলো, যুক্তরাষ্ট্রই আসলে এর পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল।
সমস্যার সূত্রপাত জুনে, যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে এবং সরাসরি মোদির সঙ্গে টেলিফোন আলাপে দাবি করেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি করিয়েছেন। ভারত সবসময় তার প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনো বহিরাগত মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান করেছে, আর মোদি এখনো ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেননি, যেমনটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন। এরপর ট্রাম্প ভারতীয় তেলের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন—এবং শুধু ভারতের ওপরই—রাশিয়ার তেল আমদানি অব্যাহত রাখার কারণে। অথচ চীন, তুরস্কসহ আরও অনেক দেশ একই রাশিয়ান তেল বিপুল পরিমাণে কিনছিল। স্পষ্টতই ট্রাম্প বিরক্ত হয়েছিলেন এই কারণে যে, চীন তার নিজের প্রয়োজনের জন্য তেল আমদানি করলেও ভারত সেই রাশিয়ান তেল পরিশোধন করে ইউরোপসহ অন্যত্র বিক্রি করে বড় মুনাফা করছিল। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ক ভয়াবহ কূটনৈতিক সংকটে পড়ে। এর চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে গত সপ্তাহান্তে তিয়ানজিনে, যেখানে শি, মোদি ও পুতিন হাত ধরাধরি করে হাসিমুখে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন। সম্মেলনের এক ফাঁকে শি ঘোষণা করলেন: “এখন সময় এসেছে ড্রাগন আর হাতি একসঙ্গে নাচবে।”
মোদির এই নতুন চীনমুখী অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের বহু দশকের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যায়। পাঁচজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ধারাবাহিকভাবে ভারতকে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদার হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যাতে চীনের শিল্প ক্ষমতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তিকে ভারসাম্য করা যায়। যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ক গত তিন দশকের অন্যতম স্থায়ী দ্বিদলীয় বৈদেশিক নীতি ছিল। আমি মনে করি ২০০৮ সালে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ. বুশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যখন পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তখন তা ভূরাজনীতিতে বড় আলোড়ন তোলে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ভারতের সঙ্গে মজবুত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে, বিশেষত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও মহাকাশ প্রযুক্তিতে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো “ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড এমার্জিং টেকনোলজি উদ্যোগ (i-CET)” এবং “ইন্ডিয়া-ইউএস ডিফেন্স এক্সেলারেশন ইকোসিস্টেম (INDUS-X)।” এই কৌশলগত সম্পর্কের কেন্দ্রে রয়েছে কোয়াড (Quad)—অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের জোট—যারা এখন শুধু পরামর্শ নয়, বরং যৌথ নৌ মহড়া, গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, উদীয়মান প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে, সবই চীনের প্রভাব ঠেকাতে।
কিন্তু ট্রাম্পের সাম্প্রতিক পদক্ষেপে এসব উদ্যোগ গতি হারাতে পারে এবং আস্থার সংকট তৈরি হতে পারে। ভারত যেমন অহংকারী, তেমনি ট্রাম্পও। এই মিশ্রণ আদর্শ নয়। ট্রাম্প টুইটে লিখেছেন: “মনে হচ্ছে আমরা ভারত ও রাশিয়াকে হারিয়ে ফেলেছি চীনের কাছে। আশা করি তারা দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ উপভোগ করবে!” যদিও এটি একটি বড় ধাক্কা, তবে এটি হয়তো স্থায়ী ভূরাজনৈতিক পরিবর্তন নয়।
<img src ='https://cms.thepapyrusbd.com/public/storage/inside-article-image/iq0vfdril.jpeg'>
ভারত-চীন সম্পর্কও জটিল। দালাই লামা ইস্যু, গালওয়ান উপত্যকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, ১৯৬২ সালের সীমান্তযুদ্ধ—এসব সমস্যার কারণে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের অবিশ্বাস রয়েছে। সরাসরি বিমান চলাচল বন্ধ, চীনা অ্যাপ যেমন টিকটক নিষিদ্ধ, হুয়াওয়ে ও জেডটিই নিষিদ্ধ—এসব উদাহরণ এরই প্রতিফলন। চীনের অর্থনৈতিক নীতি, পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও ইন্দো-প্যাসিফিকে আধিপত্যের প্রচেষ্টা ভারতের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য শুভ নয়।
ভারত দীর্ঘদিন ধরেই পরাশক্তিগুলোর প্রতিযোগিতা কাজে লাগাতে অভ্যস্ত। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় এটি নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করে। জওহরলাল নেহরু একবার বলেছিলেন: “আমরা ক্ষমতার রাজনীতির বাইরে থাকতে চাই, যা অতীতে বিশ্বযুদ্ধ ডেকে এনেছিল এবং আবারও বৃহত্তর বিপর্যয় আনতে পারে।” এই কৌশলে ভারত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেছে।
আজও ভারতে নিরপেক্ষতার নীতি জীবিত আছে। ট্রাম্প হয়তো এ নীতিকে আরও জোরদার করবেন। তবে মনে রাখা জরুরি যে, গত তিন দশকের যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ক আসলে ভারতের পুরোনো কৌশলের ব্যতিক্রম ছিল। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর যেমন বলেছেন, “আমাদের এমন কিছু চাই যা স্থিতিশীল, তবে একই সঙ্গে বর্তমান বিশ্বের প্রতিফলন ঘটায়, ১৯৪৫–এর পর পশ্চিমের পক্ষে তৈরি নিয়ম নয়।”
একই সময়ে, এসসিও ও ব্রিকসের মতো সংগঠনগুলো আসলে কার্যকর জোট গড়তে বা বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে পাল্টাতে সক্ষম নয়। তিয়ানজিনে প্রদর্শিত সৌহার্দ্য বাস্তবিক সহযোগিতায় খুব কমই রূপ নেয়, যেমনটি ন্যাটোর ক্ষেত্রে দেখা যায়।
এখন যখন একমেরু মুহূর্ত পেছনে চলে যাচ্ছে, তখন ভারত-চীন-রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ভারতের অবস্থান আসন্ন বৈশ্বিক ব্যবস্থার দিকনির্দেশনা দেখায়। ভবিষ্যৎ কেবল দ্বিমেরু বা বহুমেরু বিশ্ব নয়, বরং খণ্ডিত ও বহুপাক্ষিক জোটের সমন্বয় হতে পারে। এসব “আকাঙ্ক্ষীদের জোট” গঠিত হবে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে—হোক তা বাণিজ্য, প্রযুক্তি বা নিরাপত্তা। এখন প্রশ্ন হলো, এই নতুন বাস্তবতায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কী হবে—মিত্র হিসেবে, অংশীদার হিসেবে, নাকি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে।
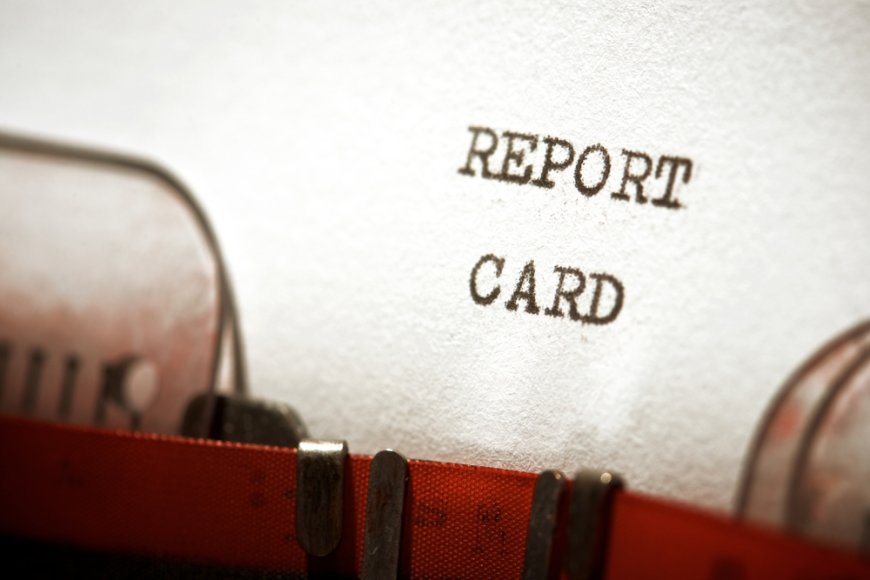


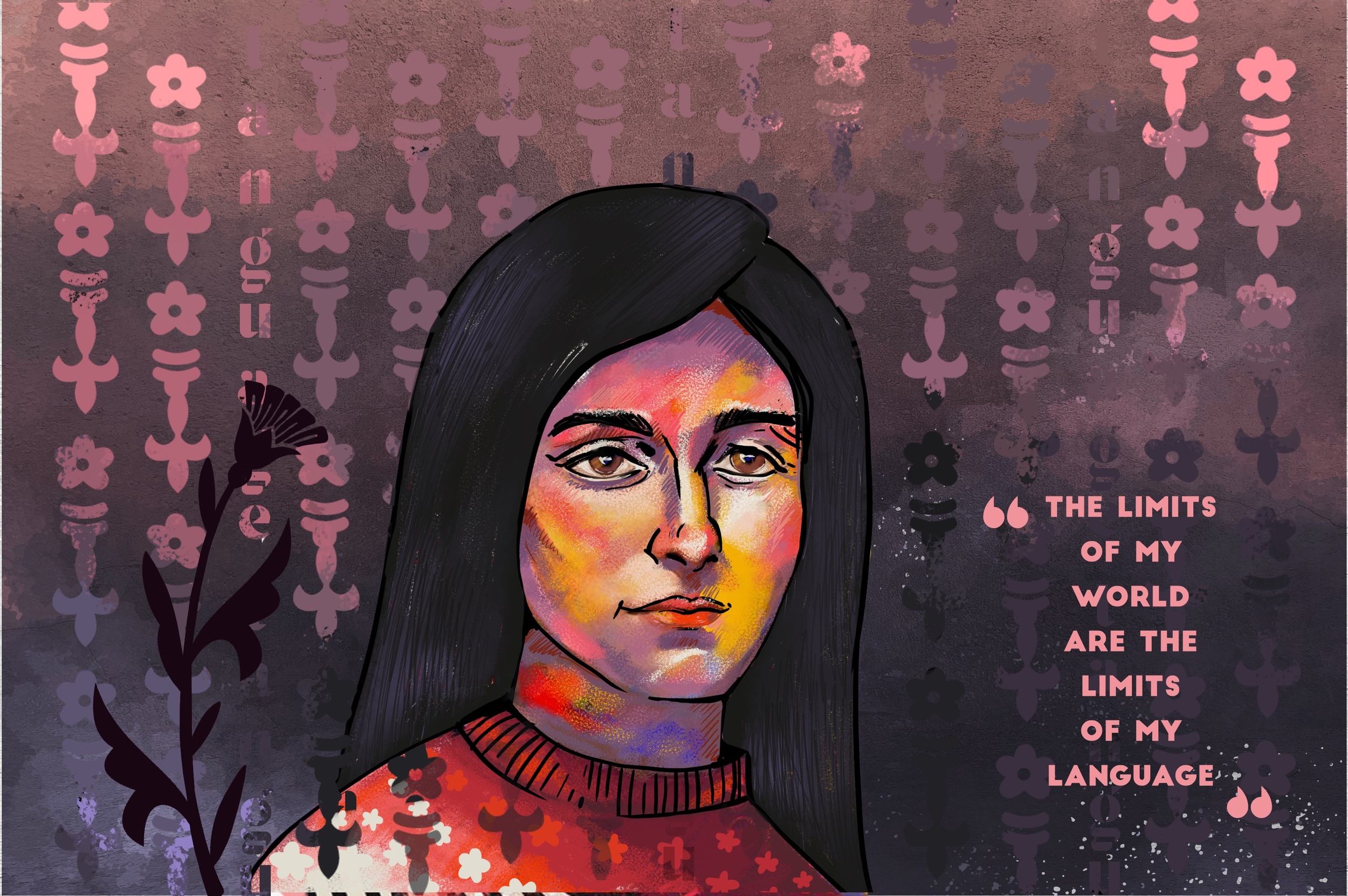



Comments