ওয়াশিংটনের দক্ষিণ এশিয়া নীতি এখন দিকভ্রান্ত। গত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা ভারতকে গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে চীনের পাল্টা ভারসাম্যকারী হিসাবে দেখেছেন এবং নয়া দিল্লিকে বেইজিংয়ের সঙ্গে বৃহত্তর প্রতিযোগিতায় স্থাপন করতে চেয়েছেন। একই সময়ে, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান নিয়ে হতাশ হয়েছে—শীতল যুদ্ধের সময়কার মিত্র হলেও ইসলামাবাদকে এখন তারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে দেখে। পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠতাও যুক্তরাষ্ট্রকে অখুশি করেছে, কারণ বেইজিং অবকাঠামো বিনিয়োগ ও সামরিক সরঞ্জামের প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে ইসলামাবাদের জন্য।
কিন্তু ভারতের ওপর যে বাজি ধরেছিল যুক্তরাষ্ট্র, সেটি ফলপ্রসূ হয়নি। দুই দশক পরও ভারত আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দের সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হতে অনিচ্ছুক এবং অক্ষম রয়ে গেছে। এ বছর দুই দেশের সম্পর্ক টানাপোড়েনে পড়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ভারতের বহুমেরুতা-অন্বেষণ—অর্থাৎ এমন এক বিশ্ব যেখানে না কোনো একক সুপারপাওয়ার আধিপত্য করবে, না দুই বৃহৎ শক্তির দ্বন্দ্বে সাজানো থাকবে—ওয়াশিংটনকে অখুশি করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও এতে ভারতের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। রাশিয়ান তেল আমদানির কারণে আগস্টে ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন, যা এখন পর্যন্ত কোনো দেশের ওপর সবচেয়ে বেশি। পরিস্থিতি আরও জটিল হয় যখন নয়াদিল্লি বেইজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের ইঙ্গিত দেয়, আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক বৈঠক করেন।
অন্যদিকে, পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে আশ্চর্যজনক উষ্ণতা ফিরে এসেছে। জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর ট্রাম্প পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক উষ্ণ করেছেন। মার্চে তিনি প্রশংসা করেন ইসলামাবাদের একটি অভিযানকে, যেখানে ২০২১ সালের কাবুল বিস্ফোরণে জড়িত সন্দেহভাজন আইএস জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল—সে ঘটনায় ১৩ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছিলেন। মে মাসে তিনি দাবি করেন, চার দিনের ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামিয়ে দিয়েছেন, যা ভয়াবহভাবে বাড়তে পারত। ট্রাম্প ঘোষণা করেন, “আমরা একটি পারমাণবিক সংঘাত থামিয়েছি। আমি মনে করি এটি খুব খারাপ পারমাণবিক যুদ্ধ হতে পারত।” এরপর থেকে তিনি বারবার দাবি করেছেন, এক ভয়াবহ বিপর্যয় ঠেকিয়েছেন; এমনকি পাকিস্তানি কর্মকর্তারা তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীতও করেন। ভারত অবশ্য কোনো বাইরের মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অস্বীকার করেছে যে এমন কোনো হস্তক্ষেপ ঘটেছিল। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, জুনে ট্রাম্প মোদিকে অনুরোধ করেছিলেন পাকিস্তানি নেতাদের মতো তিনিও যেন তাঁকে নোবেলের জন্য মনোনয়ন দেন। মোদি অস্বীকার করেন এবং তারপর থেকে দুজনের আর কথা হয়নি।
গ্রীষ্মে ট্রাম্প পাকিস্তানকে আরও কাছে টানেন। জুনে তিনি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানান। জুলাইয়ে ইসলামাবাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন, যেখানে পাকিস্তান মার্কিন কোম্পানিগুলোকে তেল অনুসন্ধানের অনুমতি দিলে শুল্কহার তুলনামূলক কম, ১৯ শতাংশে রাখা হয়। সামগ্রিকভাবে, পাকিস্তানের সঙ্গে এই উষ্ণতা ওয়াশিংটনের দক্ষিণ এশিয়া নীতির জন্য ইতিবাচক ইঙ্গিত। ভারতের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্র আসলে দক্ষিণ এশিয়ার অনেক প্রতিবেশী দেশকে, বিশেষত পাকিস্তানকে, আরও চীনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এখন সময় এসেছে ওয়াশিংটনের প্রতিশ্রুতি পুনর্বিন্যাস করার। ভারতকে পুরোপুরি ত্যাগ না করেও যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের সঙ্গে সহযোগিতার পথ খুঁজে নিতে পারে—বিশেষত আঞ্চলিক সংযোগ উন্নয়নে। এতে দক্ষিণ এশিয়া যুক্তরাষ্ট্র-চীন দ্বন্দ্বের যুদ্ধক্ষেত্র হওয়ার বদলে, বাস্তববাদী সহাবস্থানের ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। কেবল ভারতের দিকে ঝুঁকে থাকা বর্তমান মার্কিন নীতি দক্ষিণ এশিয়ায় বিভাজন গভীর করবে। এতে শুধু ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের সম্ভাবনা বাড়বে না, বরং যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে একযোগে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার কৌশলগত লক্ষ্য থেকেও বঞ্চিত হবে।
<img src ='https://cms.thepapyrusbd.com/public/storage/inside-article-image/wtvpt48b5.jpeg'>
ভুল পছন্দ
ওয়াশিংটনের ভারতের ওপর কৌশলগত বাজির মূল উদ্দেশ্য ছিল চীনের মোকাবিলায় ভারতকে দাঁড় করানো। বিল ক্লিনটনের সময় থেকে শুরু করে প্রতিটি মার্কিন প্রশাসন ভারতকে বেইজিংয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সক্ষম শক্তি হিসেবে দেখেছে। ভারতকে প্রলুব্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্র বৃহৎ অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তি চুক্তি করেছে, ভারতের নিরাপত্তা প্রদানকারী শক্তি হওয়ার পথে সহায়তা করেছে। ২০০৮ সালে ভারতের সঙ্গে নজিরবিহীন অসামরিক পারমাণবিক চুক্তি করেছে, যদিও ভারত কখনো পারমাণবিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে (NPT) স্বাক্ষর করেনি। এমনকি ইরানের চাবাহার বন্দরে ভারতের বিনিয়োগ, ইরানি তেল কেনা, কিংবা রাশিয়ার এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র কেনার পরও ভারতকে শাস্তি দেয়নি। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ চাওয়াতেও যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পাশে থেকেছে।
কিন্তু এত কিছুর পরও ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশা পূরণ করেনি। বিশ্লেষক অ্যাশলি টেলিস সম্প্রতি লিখেছেন, ভারতের বহুমেরু নীতিই তাকে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে। উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়ার ২০২২ সালে ইউক্রেন আক্রমণের বিষয়ে ভারত নিরপেক্ষ থেকেছে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলার নির্ভরতা কমাতে নানা উদ্যোগে অংশ নিয়েছে। ভারতের এই অবস্থান কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের দীর্ঘ ঐতিহ্যের ফল, যা সহজে বদলাবে না। এর ফলে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ভাঙন বাড়ছে। ভারত একাই চীনের মোকাবিলা করতে অক্ষম, অথচ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব তার অবস্থানকে আরও দুর্বল করছে।
পাকিস্তানের সঙ্গে টালমাটাল সম্পর্ক
ভারত ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার আরেক দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা করতে পারে—পাকিস্তান। তবে গত দুই দশকে এই সম্পর্ক ছিল বৈপরীত্যে ভরা। ৯/১১ পর পাকিস্তান একদিকে আফগানিস্তানে মার্কিন অভিযানের সম্মুখসারির মিত্র ছিল, অন্যদিকে তালেবানকে গোপনে সমর্থনের অভিযোগ পেয়েছে। ২০১১ সালে ওসামা বিন লাদেনের পাকিস্তানে অবস্থান ও মার্কিন অভিযানে তার নিহত হওয়া এই অবিশ্বাস চূড়ান্ত করে। আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর (২০২১), বাইডেন প্রশাসন ইসলামাবাদের সঙ্গে কৌশলগত বিচ্ছিন্নতায় যায়।
তবে সাম্প্রতিক সময়ে, বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামাতে ট্রাম্পের ভূমিকার পর সম্পর্ক আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। জুনে ট্রাম্প সরাসরি পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে বসেন—যা নজিরবিহীন। একইসঙ্গে ভারতকে কঠোরভাবে চাপে রাখছেন তিনি।
ভুল অনুমান
ট্রাম্পের অধীনে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ায় ভিন্নভাবে ভাবতে শুরু করেছে। এতদিন যুক্তরাষ্ট্র তিনটি ভুল অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে নীতি করেছে:
১. ভারত অবধারিতভাবে চীনের পাল্লা দেওয়ার মতো শক্তিশালী হবে।
২. পাকিস্তান অবধারিতভাবে চীনের দিকে ঝুঁকবে।
৩. আফগানিস্তান ইস্যুতে অসন্তোষের কারণে পাকিস্তান আর কখনো নির্ভরযোগ্য মিত্র হতে পারবে না।
কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। ভারতের প্রতি মার্কিন সমর্থন আসলে তাকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও আক্রমণাত্মক করেছে—২০১৯ ও ২০২৫ সালের সংঘাতে ভারতের সামরিক হামলা গভীরতর হয়েছে, এমনকি পাকিস্তানে হত্যাকাণ্ড চালানোর অভিযোগও উঠেছে। এর ফলে পাকিস্তান আরও চীনের দিকে ঝুঁকেছে, চীনা অস্ত্র ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করছে। সাম্প্রতিক সংঘাতে পাকিস্তান ভারতীয় বিমান প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে, যা দেখিয়েছে ভারত-পাকিস্তান শক্তির ভারসাম্যে নতুন মাত্রা এসেছে।
<img src ='https://cms.thepapyrusbd.com/public/storage/inside-article-image/kxrxjv8t6.jpg'>
সহাবস্থান, প্রতিযোগিতা নয়
পাকিস্তান-চীন সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রকে আতঙ্কিত করলেও, ইসলামাবাদ আসলে দুই পক্ষকেই ভারসাম্য রাখতে চায়। ২০২২ সালে প্রণীত জাতীয় নিরাপত্তা নীতিতে পাকিস্তান স্পষ্ট করেছে, কোনো ভূ-রাজনৈতিক শিবিরে পুরোপুরি যাবে না। তাদের অর্থনীতি একসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ওপর নির্ভরশীল।
এই অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সুযোগও বটে। শীতল যুদ্ধে যেমন পাকিস্তান নিক্সনের চীন সফরে সেতুবন্ধন করেছিল, তেমনি আবারও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আঞ্চলিক যোগাযোগ অবকাঠামোতে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ বিনিয়োগ দক্ষিণ এশিয়াকে সহযোগিতার মডেল বানাতে পারে।
পাকিস্তানের বিশাল খনিজ সম্পদ, বিশেষত রেকো দিক খনি (তামা ও সোনার মজুদ) যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়ের আগ্রহের কেন্দ্র। বেলুচিস্তানের অস্থিতিশীলতা কমাতে যৌথ উদ্যোগ পাকিস্তানকে সহায়তা করতে পারে।
অবশেষে, যুক্তরাষ্ট্রকে মেনে নিতে হবে—পাকিস্তান চীনকে পুরোপুরি ছেড়ে আসবে না, যেমন পাকিস্তানকেও মানতে হবে—ভারত যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারই থাকবে। তবে নতুন এক বাস্তববাদী সহাবস্থান হয়তো দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সর্বোত্তম ফলাফল এনে দিতে পারে।
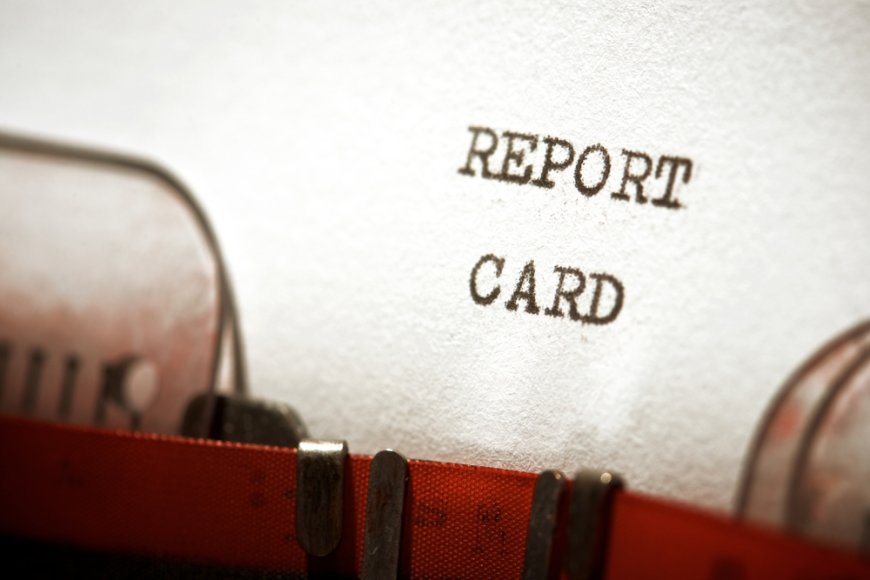


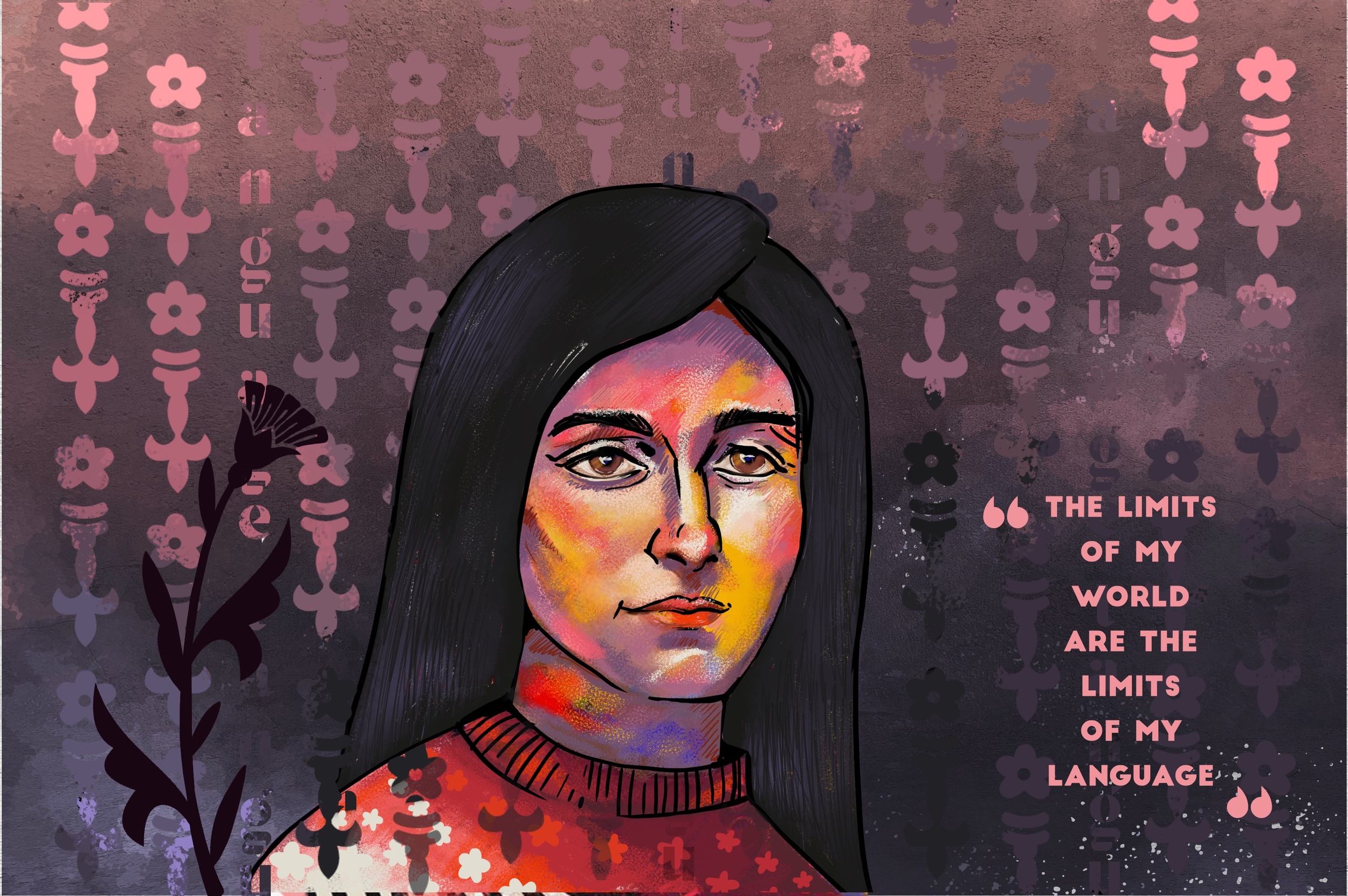



Comments