বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কক্সবাজারে ছড়িয়ে থাকা শরণার্থী শিবিরগুলো এখনো এক মিলিয়নের বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে—যারা মিয়ানমার থেকে নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার হয়ে পালিয়ে এসেছে। ২০১৭ সাল থেকে শুরু হওয়া এই সংকট এখন বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি শরণার্থী পরিস্থিতিগুলোর একটি। রোহিঙ্গাদের মর্যাদাপূর্ণ ও স্বেচ্ছামূলকভাবে মিয়ানমারে ফেরত যাওয়ার সম্ভাবনা এখনও অধরা।
এই প্রেক্ষাপটে, মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকরা “মানবিক করিডর” গঠনের সম্ভাব্যতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান আলোচনা করছেন। এটি একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পথ, যা ত্রাণ সহায়তা ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবাসনকে সহায়তা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এই ধারণা যেমন আশার আলো জাগায়, তেমনি এটি রাজনৈতিক বিতর্কেরও জন্ম দেয়। করিডরের প্রভাব শুধু মানবিক সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারে।
এই প্রবন্ধে আমরা এই ইস্যুর পূর্ণ মাত্রা—রাজনৈতিক স্বার্থ, নিরাপত্তা ঝুঁকি, ঐতিহাসিক উদাহরণ এবং এই করিডরের মাধ্যমে কীভাবে এই সংকটের গতিপথ বদলানো যায়—তা বিশ্লেষণ করব।
মানবিক করিডর কী?
সাধারানত মানবিক করিডর বলতে বোঝায় একটি অস্থায়ী নিরাপদ অঞ্চল বা পথ, যা জরুরি পরিস্থিতিতে—যেমন যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়—মানবিক সহায়তা ও সাধারণ মানুষের নিরাপদ চলাচলের জন্য তৈরি হয়। এই করিডর সাধারণত জাতিসংঘ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সমর্থন পায় এবং পরিচালিত হয়ে থাকে। যুদ্ধ বিদ্ধস্ত অনেক দেশেই মানবিক করিডর এর ব্যবস্থা আমরা দেখতে পায়। নিচে কিছু উধাহরণ থাকবে। তবে প্রশ্ন হলো যদি একটি দেশে যুদ্ধ জড়িত থাকে কিন্তু ওপর একটি দেশ যুদ্ধে জড়িত না থাকে তখন যেই দেশের মধ্য দিয়ে করিডর হচ্ছে সেই দেশের কি কোন বিপদ থাকে? এরকম উদাহরণ কি আমরা পৃথিবীতে আর কখনো দেখেছি?
উপরোক্ত অবস্থায় মানবিক করিডর করতে হলে অবশ্যই অবশ্যই কিছু জিনিস মাথায় রেখেই এগুতে হবে।
১। নিরাপত্তা: করিডরটি অবশ্যই দুই দেশের সরকারের মাঝে একটি বোঝাপড়ার মাধ্যমে হতে হবে। সাধারণ নাগরিকদের জন্য নিরাপদ করতে হয় যাতে তারা যুদ্ধের এলাকা থেকে সরে যেতে পারে এবং ত্রাণ সহায়তা পেতে পারে। এতে করে যেই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো—যেমন সরকার, বিদ্রোহী গোষ্ঠী বা আন্তর্জাতিক সংস্থা—এই করিডর ব্যবহারের অনুমতি দেয়।
২। মানবিক সহায়তা: করিডর ব্যবহার করে যেনো শুধুমাত্র খাদ্য, ওষুধ, পানি, চিকিৎসা সহায়তা ইত্যাদি সংকটাপন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া হয়। কারন কিছু ষড়যন্ত্রতত্ত্ব সবসময়ই এই সকল মানবিক করিডর নিয়ে থাকে। এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো করিডর ব্যবহার করে সামরিক অস্ত্র, গোয়েন্দা তথ্যের অবাধ বিচরণসহ মাদকের মতো জীবনহানীর ব্যবহার বিশেষভাবে আলোচিত।
বাংলাদেশ-মিয়ানমার করিডরের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব
বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে, বিশেষ করে রাখাইন রাজ্যের মধ্য দিয়ে একটি মানবিক করিডোর প্রতিষ্ঠার ধারণাটি সরাসরি দুটি আঞ্চলিক শক্তিধর দেশ - ভারত ও চীনের কৌশলগত স্বার্থের সাথে জড়িত। আঞ্চলিক ক্ষমতার এই টানাপোড়েন কীভাবে কাজ করতে পারে তা নিচে তুলে ধরা হলো:
চীনের দৃষ্টিকোণ:
কৌশলগত ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই): চীন মিয়ানমারের অবকাঠামো খাতে, বিশেষ করে চীন-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোরের (সিএমইসি) মাধ্যমে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে। কিয়াকপিউ গভীর সমুদ্রবন্দর এবং সংশ্লিষ্ট তেল ও গ্যাস পাইপলাইন রাখাইন রাজ্যের মধ্য দিয়ে গেছে, যে অঞ্চলটি করিডোরের জন্য প্রস্তাবিত। কোনো আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান বা মানবিক করিডোরের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ চীনের কৌশলগত সম্পদের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
রাজনৈতিক জোট: চীন তার বিনিয়োগ রক্ষার জন্য মিয়ানমারের সামরিক সরকারকে সমর্থন করে। জাতিসংঘ বা পশ্চিমা শক্তিগুলোর সম্পৃক্ততায় কোনো করিডোর পশ্চিমা হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যা চীন কূটনৈতিকভাবে বা জাতিসংঘের ভেটোর মাধ্যমে বিরোধিতা করবে।
ভারতের দৃষ্টিকোণ:
সংযোগ ও আঞ্চলিক প্রভাব কালাদান মাল্টি-মোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রোজেক্ট: ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে বঙ্গোপসাগরের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য রাখাইনের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি নির্মাণ করছে। রাখাইনের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ভারতের "অ্যাক্ট ইস্ট" নীতি এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য স্বার্থের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
চীনের প্রভাবের ভারসাম্য রক্ষা: ভারত মিয়ানমারকে বঙ্গোপসাগরে চীনের প্রভাবের বিরুদ্ধে একটি কৌশলগত বাফার হিসেবে দেখে। করিডোর আলোচনায় চীন ব্যাপকভাবে জড়িত থাকলে, ভারত প্রভাবের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃহত্তর আসিয়ান বা জাতিসংঘ-নেতৃত্বাধীন ভূমিকার জন্য চাপ দিতে পারে।
<img src ='https://cms.thepapyrusbd.com/public/storage/inside-article-image/ggw1qovw4.jpg'>
নিচে একটি টেবিলের মাধ্যমে আরও বিস্তারিতভাবে দেখানো হলোঃ
| দিক | ভারত | চীন |
| রাখাইনে প্রধান কৌশলগত প্রকল্প | কালাদান মাল্টি-মোডাল ট্রানজিট প্রকল্প যা অভ্যন্তরীণ জলপথ ও সড়কের মাধ্যমে মিজোরামকে রাখাইনের সিটওয়ে বন্দরের সাথে যুক্ত করে। | চীন-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোর (সিএমইসি) যার মধ্যে কিয়াউকফিউ গভীর সমুদ্রবন্দর এবং রায়হানেক পথে সংযোগকারী তেল-গ্যাস পাইপলাইনের অন্তর্ভুক্ত। |
| প্রাথমিক উদ্দেশ্য | পূর্ব-পূর্ব এশিয়ার সাথে সংযোগ বৃদ্ধি করা; আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধি করা; উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক শক্তিশালী করা। | - জুঝিয়াং প্রদেশসহ পথ সুরক্ষিত করা; - বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) সম্প্রসারণ; - জেলসপাসের প্রয়েশশিক্ষার লাভ করা। |
| করিডোর তদারকির বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি | বহুপাক্ষিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ বা আসিয়ান-নেতৃত্বাধীন তদারকির পক্ষে। | ১। সীমিত আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততাকে অগ্রাধিকার দেয়; ২। বিআরআই সম্পদের কাছে পশ্চিমা/জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে। |
| মিয়ানমারের জান্তার সাথে সম্পর্ক | ১। কূটনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত তবে মানবাধিকার ইস্যুতে সচেতন; ২। গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের উৎসাহিত করে। | ১। দৃঢ় অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক; ২।স্থিতিশীলতা ও বিনিয়োগ নিরাপত্তার জন্য জান্তার শক্তিশালী সমর্থক। |
| ঝুঁকি উপলব্ধি | করিডোর আঞ্চলিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং চীনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে একটি ভূ-রাজনৈতিক সুযোগ হতে পারে। | করিডোর বিআরআই অবকাঠামোর উপর নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করতে পারে এবং শাসনের অস্থিরতা প্রকাশ করতে পারে। |
| সম্ভাব্য উদ্বেগ | ১। কালাদান রুটের কাছে নিরাপত্তা ঝুঁকি; ২। উত্তর-পূর্ব ভারতে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। | সংবেদনশীল প্রকল্পের কাছে বিদেশী পর্যবেক্ষণ এবং সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভয়। |
| রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়ে অবস্থান | কূটনৈতিক উপায়ে স্বেচ্ছায় ও নিরাপদে প্রত্যাবাসনের সমর্থন করে। | ১। নীরবতা বজায় রাখে বা সীমিতভাবে জড়িত থাকে; ২। শরণার্থী সমস্যার চেয়ে স্থিতিশীলতাকে অগ্রাধিকার দেয়। |
| করিডোর আলোচনায় পছন্দের ভূমিকা | গণতান্ত্রিক ও মানবিক লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে আলোচনায় পর্যবেক্ষক এর ভূমিকা পালন করতে চায়। | পর্দার আড়ালে প্রভাব বিস্তারকারী, কৌশলগত অবকাঠামো রক্ষা করে এবং বিশ্বব্যাপী মনোযোগ কমিয়ে রাখে। |
মানবিক করিডোরে নিরাপত্তা ঝুঁকি: সীমান্তে স্থিতিশীলতা ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়
বাংলাদেশ-মিয়ানমার প্রস্তাবিত মানবিক করিডোর নিয়ে কূটনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি একটি গুরুতর দিক এখনো স্পষ্টভাবে আলোচনায় আসেনি—সেটি হচ্ছে এর নিরাপত্তা ঝুঁকি। দীর্ঘদিন ধরে অস্থিতিশীল সীমান্ত ও সংঘাতময় রাজনৈতিক বাস্তবতা করিডোরের কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। তাই এই করিডোরের সফল বাস্তবায়নের জন্য নিরাপত্তার বিষয়টি এখন প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।
সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে ইতোমধ্যেই সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সক্রিয় উপস্থিতি একটি বড় উদ্বেগের কারণ। বিশেষ করে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (ARSA) এবং অন্যান্য স্থানীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী করিডোরের সুযোগ নিয়ে নিজেদের কার্যক্রম বিস্তৃত করতে পারে। এই গোষ্ঠীগুলো মানবিক করিডোরকে একটি কৌশলগত পথ হিসেবে ব্যবহার করে নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটাতে পারে, যার ফলে সাধারণ জনগণ আবারও নতুন করে বিপদের মুখে পড়বে। এর সঙ্গে জড়িত আরেকটি বড় উদ্বেগ হলো—অস্ত্র ও মানব পাচার। এই সীমান্ত এলাকায় ইতিহাস জুড়েই চোরাচালান ও অপরাধমূলক নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে। মানবিক করিডোর চালু হলে তার ছায়াতলে অস্ত্র ও মানব পাচারকারীরা সক্রিয় হতে পারে। এটি শুধু সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য নয়, বরং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্যও হুমকি হয়ে উঠবে।
এছাড়া করিডোর সংলগ্ন মিয়ানমার অংশে এখনো বিভিন্ন জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী সক্রিয়, বিশেষ করে আরাকান আর্মি। মিয়ানমার বাহিনী ও এসব গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়মিত সংঘর্ষ হয়, যা করিডোর পরিচালনার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। সামান্য উত্তেজনাও যদি ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে পুরো করিডোর ব্যবস্থাই অনিরাপদ হয়ে পড়বে এবং সাধারণ মানুষ সেই করিডোর ব্যবহার করতে সাহস পাবে না।
এই পরিস্থিতিতে করিডোরের নিরাপত্তা নিশ্চিতে চাই একটি নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী বাহিনীর উপস্থিতি। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী এই দায়িত্ব নিতে পারে, যারা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশিক্ষিত এবং নিরপেক্ষভাবে অঞ্চল পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা রক্ষা করতে সক্ষম। বিকল্প হিসেবে আসিয়ান পর্যবেক্ষক দলও এই দায়িত্বে নিযুক্ত হতে পারে, বিশেষ করে যদি সদস্যদেশগুলোর মধ্যে সম্মতি থাকে।
তবে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন, মানবিক করিডোর যেন কোনোভাবেই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের গোপন পথ হয়ে না ওঠে, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি। জনগণের বিশ্বাস অর্জনই হবে করিডোর ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। আর সে বিশ্বাস গড়ে উঠবে তখনই, যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং সীমান্তে একটি স্থিতিশীল পরিবেশ গড়ে উঠবে। এই নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা না করলে মানবিক করিডোর একটি মহৎ ধারণা হয়েও বাস্তবে অকার্যকর এবং বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই এখনই সময়—উদ্যোগের পাশাপাশি বাস্তব প্রস্তুতি নেওয়ার।
করিডরের সম্ভাব্য সুফল
এটি একটি পর্যবেক্ষণভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে আরাকান আর্মিদের সাহায্যের মাধ্যমে তাদের সাথে একটি চুক্তি বাস্তবায়ন করে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন শুরু করা যেতে পারে। প্রথমে পাইলট প্রকল্পের মাধ্যম দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। যারা ফিরতে চায় না, তাদের জন্য করিডর খাদ্য, ওষুধ ও অন্যান্য পরিষেবা পৌঁছাতে সহায়ক হতে পারে।
এর সাথে এই ধরনের উদ্যোগ জাতিসংঘ বা আসিয়ানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হলে মিয়ানমারের ওপর বাংলাদেশ ডিপ্লোম্যাটিক চাপ বাড়াতে পারবে। এরই ফলশ্রুতিতে রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে রোহিঙ্গারা তারা তাদের দেশে ফিরে যেতে একটা বাস্তব পথ খুলে যাওয়ার সমুহ সম্ভাবনা থেকেই যায়। কারন আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রোহিঙ্গা সংকট বর্তমানে গাজা ইসরাইল এবং রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের কারনে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছে। এই করিডর উন্মোচন বিশ্বকে আবার রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় আবার যুক্ত করবে।
চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি
এই মানবিককরিডরকে যদি বিশ্ব পরাশক্তির খেলার মাঠ তথা ভু-রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অত্যধিক মাত্রায় সামরিকীকরন করে করিডরের নামে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিনত করা হয় তাহলে এই করিডর নিরপেক্ষতা হারাবে এবং বাংলাদেশ আরেকটি মায়ানমার এর মতো গৃহযুদ্ধে পরিনত হতে সময় লাগবে না।
গত বছরের বর্ষাবিপ্লবের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা এমনেই অনেক অনেক নাজুক। দেশে এখনো কোন পলিটিকাল সরকার গঠিত হয় নাই। শান্তিতে নোবেল জয়ী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস এর অন্তর্বর্তী সরকার বর্ষা বিপ্লবের পর দেশের মধ্যে অনেকগুলো সংস্কার নিয়ে রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের বিভেদের মধ্যে আছে। সেই সাথে দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরাসরি এই করিডরের বিপক্ষে কড়া সমালচনায় লিপ্ত। তাদের মতে এইরকম করিডর তৈরি ও পরিচালনা করতে যে পরিমাণ সম্পদ ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন সেটি কেবল গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোন সরকারই এই রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
কিন্তু তারা ভুলে গেছে যে ১৬ বছরের দীর্ঘ পতিত হাসিনা সরকারের পর যে বর্ষা বিপ্লবের মাধ্যম দিয়ে প্রফেসর ইউনুস ক্ষমতায় বসেছে তাঁর চেয়ে বড় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর একটিও হতে পারে না।
বৈশ্বিক উদাহরণ থেকে শিক্ষা
সিরিয়াঃ
সিরিয়া এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এক মর্মান্তিক গৃহযুদ্ধের অভ্যন্তরীণ সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই সময়ে সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে উঠে এসেছে "মানবিক করিডোর" নামক ধারণাটি। মানবিক করিডোর বলতে বোঝায় এমন কিছু নির্ধারিত নিরাপদ পথ, যেগুলো দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে সাধারণ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়, চিকিৎসাসেবা ও খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়। যদিও এই উদ্যোগ মানবাধিকারের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তবে এর বাস্তবায়ন হয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা, অবিশ্বাস ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে।
সিরিয়ার যুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন সময়ে জাতিসংঘ, রেড ক্রস ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার চাপে সিরিয়ান সরকার এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সাময়িক সমঝোতার ভিত্তিতে মানবিক করিডোর খোলা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি করিডোরের মধ্যে রয়েছে ২০১৬ সালের আলেপ্পো করিডোর, ২০১৮ সালে রাশিয়া-সমর্থিত ইস্টার্ন ঘৌতা করিডোর, এবং বর্তমানে নিয়মিত হামলার শিকার ইদলিবে প্রস্তাবিত করিডোর। এসব করিডোরের মাধ্যমে কিছু মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন, তবে এর নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে।
মূল সমস্যা দেখা দিয়েছে করিডোর ব্যবহারে সাধারণ মানুষের ভয় এবং অনিশ্চয়তা নিয়ে। অনেকেই বিশ্বাস করতেন না যে সরকার-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রবেশের পর তাঁরা নিরাপদ থাকবেন। এমনকি, কিছু ক্ষেত্রে করিডোরে হামলার ঘটনাও ঘটেছে। ফলে নিরাপত্তার অভাব ছিল স্পষ্ট। অন্যদিকে, মানবিক করিডোর অনেক সময় রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। খাদ্য ও ওষুধের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে জনগণ ও বিদ্রোহীদের উপর চাপ সৃষ্টি করার মতো ঘটনা ঘটেছে, যা মানবাধিকারের পরিপন্থী।
আন্তর্জাতিক তদারকির অভাবও এই উদ্যোগকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি ছাড়া করিডোরগুলোর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা বজায় রাখা যায়নি। অনেক সময় করিডোরগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে, কিংবা মানবিক সাহায্য বিতরণে স্বচ্ছতা ছিল না। এসব সমস্যার পাশাপাশি করিডোর ব্যবহার করে বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষদের অনেকেই আর ফিরতে পারেননি। ফলে তৈরি হয়েছে একটি দীর্ঘমেয়াদি উদ্বাস্তু সংকট, যা সিরিয়ার সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে।
বর্তমানে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস করছেন শরণার্থী ক্যাম্পে বা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। পুনর্গঠনের কাজ চলছে অত্যন্ত ধীরগতিতে, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার বিপর্যয় এখনো কাটিয়ে ওঠা যায়নি। অধিকাংশ মানুষের জীবনজুড়ে রয়েছে মানসিক আঘাত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা।
সব মিলিয়ে বলা যায়, সিরিয়ার মানবিক করিডোর স্বল্পমেয়াদে কিছু মানুষকে রক্ষা করলেও এটি একটি স্থায়ী সমাধান দিতে পারেনি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, নিরাপত্তাহীনতা ও আন্তর্জাতিক স্বচ্ছতার অভাবে এই উদ্যোগ অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে সত্যিকারের মানবিক করিডোরের জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ তদারকি, আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং রাজনৈতিক সংকটের স্থায়ী সমাধান। যুদ্ধবিধ্বস্ত জনগণের জন্য করিডোর যেন শুধুমাত্র একটি পথ না হয়ে উঠে, একটি আশ্রয়ের প্রতীক—সেই দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সমাজের ওপর বর্তায়।
<img src ='https://cms.thepapyrusbd.com/public/storage/inside-article-image/r1he7izzo.jpeg'>
ইউক্রেন
রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেন আক্রমণের পর বিশ্ব নতুন করে যুদ্ধ এবং মানবিক সংকটের এক জটিল চিত্র প্রত্যক্ষ করেছে। এই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শহরগুলোর মধ্যে মারিউপোল, সুমি এবং খারকিভ অন্যতম, যেখানে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বিভিন্ন সময়ে মানবিক করিডোর চালু করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল—যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা থেকে সাধারণ জনগণকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া এবং ন্যূনতম চিকিৎসা ও খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া।
তবে বাস্তব চিত্র ছিল ভিন্ন। এসব করিডোরের কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় যুদ্ধবিরতির চুক্তি লঙ্ঘন, নিরাপত্তাহীনতা এবং অপরিকল্পিত সমন্বয়হীনতার কারণে। বিশেষ করে মারিউপোলে, যেখানে করিডোর ঘোষণা সত্ত্বেও বারবার গোলাবর্ষণ ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। এমনকি কিছু রুটে মাইন পেতে রাখা হয়েছিল, ফলে বহু সাধারণ মানুষ এই করিডোর ব্যবহার করতে পারেননি বা সাহস পাননি। জাতিসংঘ এবং রেড ক্রসের মতে, মানবিক করিডোর সফল করতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করা আবশ্যক—নির্ধারিত সময়সূচি, সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ, এবং সর্বোপরি যাতায়াতকারীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা। কিন্তু ইউক্রেনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এসব শর্ত অনেক সময়ই মানা হয়নি। ফলে অনেক করিডোর নামমাত্র থেকে গেছে, কার্যত সাধারণ জনগণের জন্য অনিরাপদ ও অনিশ্চিত।
এই যুদ্ধের ফলে ইউক্রেন এবং ইউরোপজুড়ে যে বাস্তুচ্যুতি ঘটেছে, তার পরিমাণ বিশাল। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৬.৯ মিলিয়ন ইউক্রেনীয় ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়াও প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ ইউক্রেনের অভ্যন্তরেই বাস্তুচ্যুত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। তারা হারিয়েছে নিজেদের ঘরবাড়ি, চাকরি, শিক্ষা এবং মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ। এই বাস্তুচ্যুত জনস্রোত আশ্রয়দাতা দেশগুলোতেও নতুন সংকট তৈরি করেছে। সীমান্তবর্তী দেশগুলোতে দেখা দিয়েছে আশ্রয়ের অভাব, খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবার উপর অতিরিক্ত চাপ, এমনকি মানবপাচার ও শোষণের ঝুঁকি বেড়েছে। ফলে একটি মানবিক করিডোর শুধুমাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য নিরাপদ পথ তৈরি করলেই যথেষ্ট নয়—এর সঙ্গে থাকতে হবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন।
তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের করিডোর এবং বাংলাদেশের প্রস্তাবিত মায়ানমার করিডোর এক নয়। ইউক্রেন-রাশিয়া দুই পক্ষই যুদ্ধরত, যেখানে করিডোরের কার্যকারিতা নির্ভর করছে চুক্তির বাস্তবায়ন ও বিশ্বাসের উপর। আর বাংলাদেশ-মায়ানমার প্রেক্ষাপটে মানবিক করিডোরের প্রস্তাব এসেছে একটি একতরফা মানবিক উদ্বেগ থেকে, যেখানে বাংলাদেশ মূলত রোহিঙ্গা জনগণের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে এ উদ্যোগকে দেখছে।
সুতরাং ইউক্রেনের অভিজ্ঞতা আমাদের শেখায়—মানবিক করিডোর শুধু রাজনৈতিক বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকলে কোনো বাস্তব পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। এটি সফল করতে হলে চাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃঢ় সহায়তা, স্বচ্ছতা এবং সর্বোপরি যুদ্ধরত পক্ষগুলোর আন্তরিকতা। না হলে করিডোরগুলো হয়ে দাঁড়াবে শুধুই একটি প্রতীকি ব্যবস্থা, যার বাস্তব প্রভাব সীমিত।
<img src ='https://cms.thepapyrusbd.com/public/storage/inside-article-image/28j9nztu6.jpg'>
বাংলাদেশ-মিয়ানমার মানবিক করিডোর: আন্তর্জাতিক সহায়তা ও আঞ্চলিক সমন্বয়ই সাফল্যের চাবিকাঠি
বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার মানবিক করিডোর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এখন শুধু রাজনৈতিক আলোচনা নয়, একটি বাস্তব সম্ভাবনাও হয়ে উঠেছে। মূলত রোহিঙ্গা জনগণের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের জন্য এই করিডোরকে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে এটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক শক্তির দৃঢ় সমর্থন, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে কার্যকর সমঝোতা।
জাতিসংঘ ও ওআইসির মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা এখানে অপরিহার্য। বিশেষ করে UNHCR, IOM এবং OCHA-এর মতো সংস্থাগুলোর প্রযুক্তিগত ও মানবিক সহায়তা ছাড়া করিডোর কার্যকরভাবে পরিচালনা সম্ভব নয়। ওআইসি রাজনৈতিক চাপ ও কূটনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে প্রস্তাবকে এগিয়ে নিতে পারে। পাশাপাশি আসিয়ান, যে সংগঠনটি ঐতিহ্যগতভাবে সদস্যদেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকে, তারাও মিয়ানমার সংকটে কিছুটা ব্যতিক্রমী ভূমিকা রাখছে। রোহিঙ্গা সমস্যা ও করিডোর বাস্তবায়নে আসিয়ানের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই সংগঠনটির আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা বাড়াতে পারে।
বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটও এই প্রস্তাবকে বাস্তবায়নের দিকে ধাবিত করছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘ অবস্থান নিয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী মন্দা, আন্তর্জাতিক সহায়তার ক্রমহ্রাস এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর চাপ, সরকারকে দ্রুত সমাধানের দিকে যেতে উৎসাহিত করছে। বিশেষ করে ২০২৬ সালে বাংলাদেশের এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) থেকে উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা আরও বাড়বে, যার মধ্যে শরণার্থী ব্যবস্থাপনাও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে।
এই বাস্তবতায় একটি আদর্শ মানবিক করিডোরের রূপরেখা পরিষ্কার হওয়া জরুরি। প্রস্তাবিত করিডোরের অবস্থান হতে পারে বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে মিয়ানমারের মংডু পর্যন্ত। এটি শুধু সরাসরি প্রত্যাবাসনের পথ নয়, বরং একটি সুশৃঙ্খল, নিরাপদ ও মানবিক সহায়তা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। এই করিডোরের আওতায় জাতিসংঘের সহায়তায় পরিচালিত শরণার্থী কনভয়, চিকিৎসা সহায়তা এবং পর্যবেক্ষণকারী দল মোতায়েন থাকবে। পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব থাকতে হবে নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক পক্ষের ওপর—যেমন আসিয়ান, আইসিআরসি ও জাতিসংঘ। প্রাথমিকভাবে ছয় মাস মেয়াদি এই করিডোর চুক্তিভিত্তিক হবে, যা পরিস্থিতি অনুযায়ী নবায়নযোগ্য। এর ভিত্তি হবে একটি ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক, যেখানে বাংলাদেশের পাশাপাশি মিয়ানমার এবং জাতিসংঘ স্বাক্ষরকারী থাকবে। পর্যবেক্ষক হিসেবে চীন ও ভারতকে যুক্ত করা হলে কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হবে। তবে এই করিডোর অবশ্যই হতে হবে বেসামরিক, স্বচ্ছ এবং মানবিক; যেখানে কোনো সামরিক উপস্থিতি থাকবে না, থাকবে না জবরদস্তি বা কূটনৈতিক ফাঁকফোকরের সুযোগ। এটি হতে হবে বিশ্বাস গঠনের একটি সেতু, যেখানে রোহিঙ্গা জনগণ নিজ ইচ্ছায়, নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে তাদের জন্মভূমিতে ফিরতে পারে।
বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে একটি মানবিক করিডর কেবল একটি মানবিক বা প্রযুক্তিগত উদ্যোগ নয়—এটি একটি কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ। কিন্তু দেরি করলে ঝুঁকি আরও বাড়বে। সাহসী আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ছাড়া রোহিঙ্গারা অনির্দিষ্টকালের জন্য অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকবে। এই করিডরকে সমাধানের শেষ পথ ভাবা যাবে না—এটি হতে হবে একটি সেতু, যা রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার, বিচারিক জবাবদিহিতা ও আঞ্চলিক সংহতির দিকে নিয়ে যাবে। সিরিয়া ও ইউক্রেনের উদাহরণ আমাদের শেখায়, মানবিক করিডর তখনই কার্যকর হয়, যখন তা বিশ্বাস, স্বচ্ছতা ও যৌথ দায়িত্ববোধের উপর গড়ে ওঠে।
বাংলাদেশ-মিয়ানমার প্রসঙ্গে শুধু সম্মতিই যথেষ্ট নয়, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্বাস—এই উপাদানগুলো জরুরি, যা বর্তমানে অনুপস্থিত।
এখনই সময় সেই দায়িত্ব পালনের।
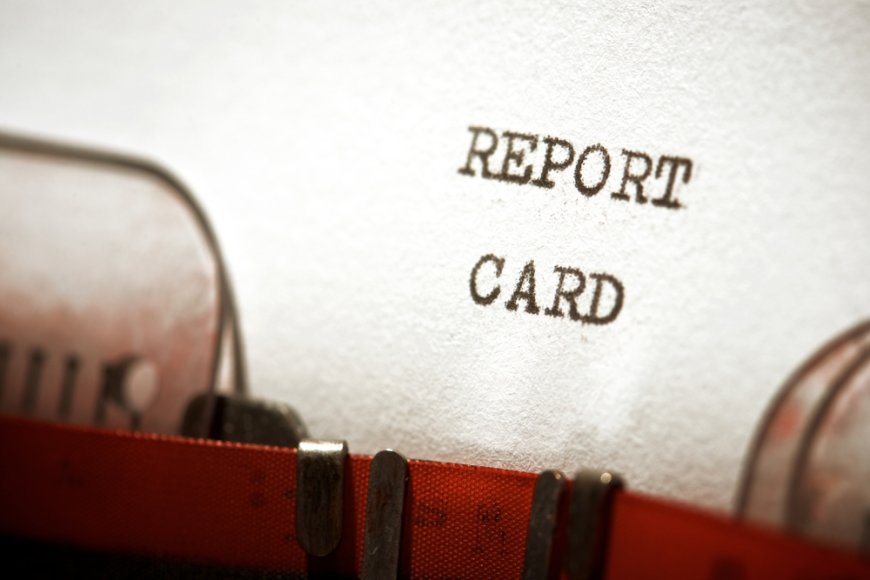


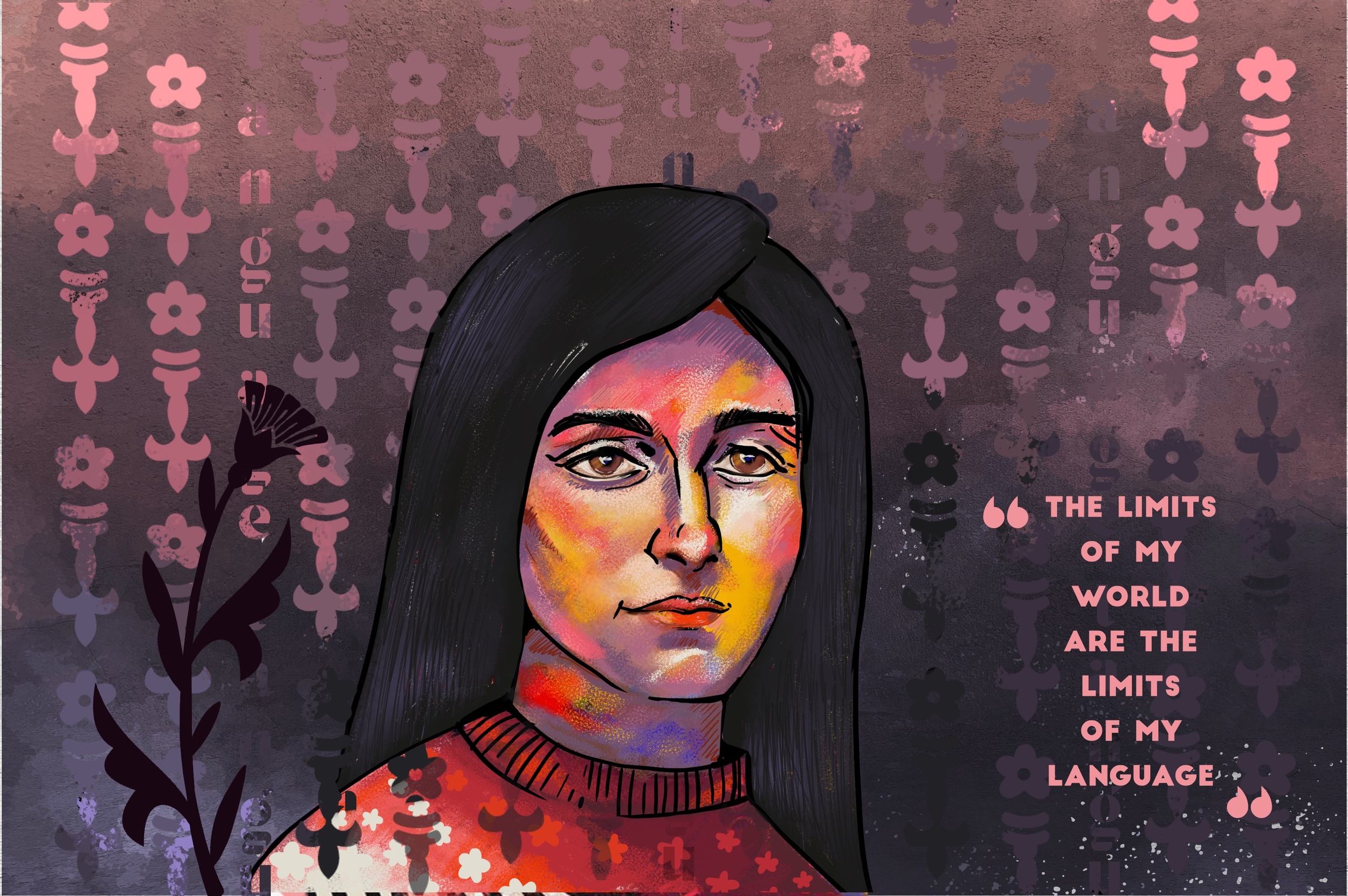



Comments